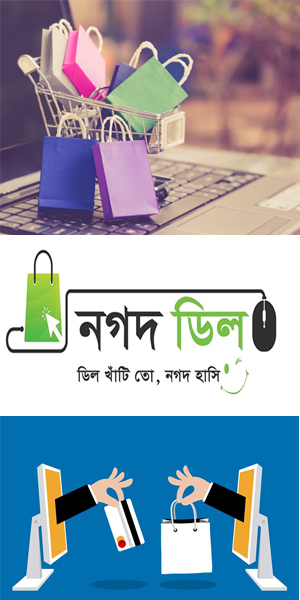“চলে যাব, সেদিন মরণ এসে অন্ধকারে আমার শরীর/ভিক্ষা করে লয়ে যাবে,- সেদিন দু’দণ্ড এই বাংলার তির-/এই নীল বাঙলার তীরে শুয়ে একা একা কী ভাবীব, হায়,—”
শরীর খুব অসুস্থ, কদিন ধরেই তেতে ছিলো অভব্য প্রতিবেশী ভাড়াটিয়ার কারণে। প্রতিদিনের মতোই ১৪ অক্টোবর বিকালে তিনি হাঁটতে বের হলেন। একা জীবনানন্দ। যখন বেরুচ্ছিলেন স্ত্রী লাবণ্য তাঁকে বেরুতে নিষেধ করলেন, শরীর অসুস্থ ছিলো কয়েকদিন ধরেই। লাবণ্যর নিষেধ না শুনেই জল দিয়ে মাথা ধুয়ে একাই বেরিয়ে যান। ফেরার সময় বাড়ির কাছের লেক মার্কেট থেকে দুটো ডাব কিনে নেন।
হাঁটতে হাঁটতে জীবনানন্দ রাসবিহারী এভিনিউ ও ল্যান্সডাউন রোডের সংযোগস্থলের প্রায় কাছাকাছি এসে গেছেন, তিনি আসছিলেন রাসবিহারী এভিনিউয়ের দক্ষিণ দিকের ফুটপাত ধরে, সংযোগস্থলে এসে ফুটপাত থেকে নেমে রাস্তা অতিক্রম করার জন্য পথে নামলেন। রাস্তার এই অংশটা বেশ চওড়া, ট্রাম যাতায়াতের জন্য রাস্তার মাঝখানে দুটো ট্রাম লাইন পাতা। ট্রাম লাইনের জমিটা ঘাসে সবুজ। তিনি ফুটপাত থেকে নেমে মোটর, বাস, ট্যাক্সি প্রভৃতির জন্য পিচ রাস্তার অংশ অতিক্রম করে ট্রাম লাইনের কাছে এলেন, মনটা কিছুটা চঞ্চল ছিলোই, ভাবলেন ট্রাম আসার আগেই লাইন পার হয়ে যেতে পারবেন, এর আগে তো একটা স্টপেজ আছেই, এসব ভাবতে ভাবতে কিছুটা অন্যমনস্ক হয়েই ট্রাম লাইন পার হতে লাগলেন। তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে, অন্ধকার অল্প অল্প করে জমছে। ট্রামটা আসছিলো, আগের স্টপেজে লোক ওঠানামা না থাকায় না থেমে জোরের সঙ্গেই চলে এলো, ছুটন্ত ট্রামটি জোরের সঙ্গেই এসে ধাক্কা দিলো কবিকে, জীবনানন্দ আর ট্রাম লাইন পার হতে পারলেন না। সঙ্গে সঙ্গে আহত ও অচৈতন্য হয়ে ট্রাম লাইনের মাঝের সেই সবুজের ওপর ছিটকে পড়লেন, ট্রামের ক্যাচারের ভিতরে দেহটা ঢুকে গেলো। রাসবিহারী এভিনিউ ও ল্যান্সডাউন রোডের সংযোগস্থলের দক্ষিণে একটা জলখাবারের দোকান ছিলো, নাম ছিলো ‘জলখাবার’। মালিক চুনীলাল দে পরে সেখানে ‘সেলি ক্যাফে’ নামে রেস্টুরেন্ট খোলেন। জীবনানন্দের দুর্ঘটনার সময় এই চুনীবাবুই শুধু প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না, তিনি ছুটে গিয়ে অনেক সাহায্যও করেছিলেন। সেই চুনীবাবুর কথায়, “একটু পরেই হঠাৎ ট্রামের একটা শব্দ, বালিগঞ্জমুখো একটা ট্রাম কাকে যেন চাপা দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই পথচারীদের অনেকেই এসে গেলেন। গিয়ে দেখি একজন লোক অচৈতন্য হয়ে ট্রামের ক্যাচারের মধ্যে পড়ে আছেন। ট্রাম দাঁড়িয়ে আছে। ট্রামের ড্রাইভার দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই ভিড়ের মাঝে গা-ঢাকা দিয়ে সরে পড়েছে। যাহোক, আমি তখনি ট্রামের তলায় ঢুকে আস্তে আস্তে তাকে বের করলাম। সমবেত জনতার দু’একজনের কথা কানে আসছিল, ট্রাম লাইনের ঘাসের উপর দিয়ে এই ভদ্রলোক আনমনে আসছিলেন। ট্রাম ড্রাইভার হর্ন দিয়েছিল, দু’একজন চিৎকার করলেও ভদ্রলোক কিসের চিন্তায় এমন বিভোর ছিলেন যে কিছুই তাঁর কানে যায়নি। যখন তাঁকে বের করা হলো, তখন তিনি অজ্ঞান। দু-তিনজনে মিলে জ্ঞানহীন জীবনানন্দকে ট্যাক্সিতে তুলে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো।” চুনীবাবু তাঁকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে রেখে এলেন, সাধারণ রোগীর মতোই পড়ে রইলেন জীবনানন্দ দাশ। পরে আত্মীয়স্বজনরা অন্য বিভাগে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও তাঁর শরীরের অবস্থার কারণে তা সম্ভব হয়নি আর। ট্রামের ধাক্কায় জীবনানন্দের বুকের কয়েকটা পাঁজর, কাঁধের হাড় এবং পায়ের হাড় ভেঙে গিয়েছিলো। ডা. বিধান রায় তাকে দেখতে গিয়ে জানিয়ে দেন যে তাঁর আর বাঁচার আশা নেই, যতদিন থাকেন একটু শান্তিতে রাখবেন। শম্ভুনাথ হাসপাতেলেই তখন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন কবি। ১৪ অক্টোবর রাত ৮টায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, ২২ অক্টোবর রাত ১১টা ৩৫ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গোটা জীবন অশান্তি ও অতৃপ্তির যন্ত্রণার ভেতরে পরিসমাপ্তি ঘটলো। সবুজ ঘাস তার প্রিয় ছিলো, অন্তিম আঘাতেও তিনি ছিটকে পড়েছিলেন সেই সবুজ ঘাসেই।
১৯৫১’র ২৮ মে ১৮৩ ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ি থেকে উত্তর বাংলার জলপাইগুড়ি শহরের তরুণ লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদক সুরজিৎ দাশগুপ্তকে চিঠিতে লিখেছিলেন যে, ‘একবার ঘুরে আসতে ইচ্ছে করে, সভাসমিতি ইত্যাদি সবকিছুর হাত সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে তোমাদের মতো দুএকজনের সাহায্যে হিমালয়, চা-বাগান ইত্যাদি দেখে আসার লোভ জেগেছে মনে।’ পঞ্চাশোর্ধ্ব কবির আরো অনেক ইচ্ছার মতোই এই ইচ্ছাও পূর্ণ হয়নি। উল্লিখিত চিঠির সূত্রেই সুরজিত বাবু তাঁর শহরের কিছু নিসর্গ দৃশ্যের ফটোগ্রাফ পাঠিয়ে দেন। ‘নগ্ন নির্জন’ শহরের ছবি। উত্তরে জীবনানন্দ লেখেন, ‘এখুনি ঝিলের পাড়ে ঘাসের ওপর আকাশের মুখোমুখি নিজেকে ছড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করছে। নদী, ঝিল, পাহাড়। বন, আকাশ। কোনো নিরালা জায়গা থেকে এসবের নিকট সম্পর্কে আসতে ভালো লাগে আমার। বসে থাকতে পারা যায় যদি এদের মধ্যে, কিংবা হেঁটে বেড়াতে পারা যায় সারাদিন, তা হলেই আমাদের সময় একটা বিশেষ দিক দিয়ে (আমার মনে হয়) সবচেয়ে ভালো কাটে।’
নির্জনতা ও বিষণ্নতা আক্রান্ত জীবনানন্দের, প্রকৃতি ও মানবতার ছায়া-আচ্ছন্ন ভালো লাগার ছোট ছোট টুকরোগুলো এমনই ছিলো। ঝিলের পাশে ঘাসের ওপর আকাশের মুখোমুখি নিজেকে ছড়িয়ে দিতে চাওয়া কবির ভালোবাসার ইচ্ছেগুলোও ছিলো ভেসে বেড়ানো মেঘের মতো; শুভ্র ও খণ্ড খণ্ড, নিঃস্বার্থ ও উচ্চাশামুক্ত। এসব ভালো লাগার ইচ্ছের অধিকাংশই ইচ্ছেপূরণের আনন্দে উত্তীর্ণ হয়নি, এই অতৃপ্তির যন্ত্রণার দহনেই দগ্ধ হয়েছেন তিনি নীরবে। নির্জন ও স্বতন্ত্র এই কবির গোটা জীবন ধরে রক্তপথ যাত্রা তাঁকে আরো স্বতন্ত্র করে দিয়েছিলো। জীবনানন্দের ৫৫ বছরের জীবনে ১৯১৯-এ ‘ব্রহ্মবাসী’ পত্রিকায় প্রকাশিত (বৈশাখ ১৩২৬) বর্ষা আবাহন কবিতা থেকে শুরু ধরলে কবিজীবন মাত্র ৩৪ বছরের, প্রকৃত বিচারে যদিও কবি জীবনানন্দের আয়ুষ্কাল আরো কম। এই ক্ষণকালের মধ্যেই তাঁর অন্তরের অনেকটা জুড়েই ছিলো নতুনের, তারুণ্যের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। এ কারণেই যখন প্রান্তবাংলা জলপাইগুড়ির তরুণেরা লিখলেন, ‘আধুনিক সাহিত্য, বিশেষত, আধুনিক বাংলা কবিতার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের মানুষদের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য একটা পত্রিকা প্রকাশ করতে চাই। আপনার একটা কবিতা চাই।’ জীবনানন্দের পর্যায়ের কবি এর উত্তরে কত অনায়াসে ‘শিরিষের ডালপালা লেগে আছে বিকালের মেঘে’ মফস্বলের নাম না জানা, না দেখা, সাক্ষাৎপরিচয়হীন সদ্য কৈশোর অতিক্রান্ত ছাত্রদের পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দেন। জীবনানন্দকে জলপাইগুড়ি আসার আমন্ত্রণ করা হয়েছিলো ‘জলার্ক’-এর তরুণদের পক্ষ থেকে। ১৯৫২’র ২০ জানুয়ারি জীবনানন্দ সুরজিত দাশগুপ্তকে এক চিঠিতে লেখেন, “জলপাইগুড়ির ওদিককার অঞ্চল, পাহাড়, নদী, জংগল বেশ দেখবার মতো, ঘুরবার মতো, ঘুরে বেড়াবার মতো, আমার খুব ইচ্ছা করে, জলপাইগুড়ির দিকে একবার যাব ভাবছি।” কিন্তু তাঁর এই ইচ্ছা অপূর্ণই থেকে যায়। ১৯৫২-তে লেখেন, ‘আমার এখন জলপাইগুড়ি যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। যেতে পারলে অবশ্য আনন্দিত হতাম।’
অসুস্থতা, বেকারত্ব, পারিবারিক অশান্তিতে বিপর্যস্ত কবি যেন সে সময় তাঁর ভালো লাগার জগৎ থেকে ক্রমেই ছিটকে যাচ্ছেন। এমনকি, কবিতাও লিখতে পারছেন না এই সময়। কবি কায়সুল হককে লেখা এই সময়ের একটি চিঠিতে তিনি একথা লিখেছিলেন। ১৯৫২ সালের ২৬ জুন তিনি জানালেন, ‘নানা কারণে মন এত চিন্তিত আছে, শরীরও এত অসুস্থ যে অনেকদিন থেকেই কিছু লিখতে পারছি না।’ আলোচ্য এই চিঠিগুলো জীবনানন্দ লিখেছিলেন ১৯৫১-৫২, যখন তাঁর অন্তরাত্মা চাইছিলো জলপাইগুড়ির মতো কোনো সবুজ নির্জনতা। যখন চারপাশ তাঁর কাছে রূঢ় হয়ে উঠছিলো। প্রতিটি ইচ্ছা ও কামনার মৃত্যু পরখ করছেন প্রতিদিন। ১৯৫০-এর ২ সেপ্টেম্বর তিনি খড়্গপুর কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন, সদ্য প্রতিষ্ঠিত কলেজে নামমাত্র মাইনে পেতেন। স্ত্রী লাবণ্য ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে বি.টি. পড়তে শুরু করেছেন এ-সময়। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ‘এলকাইনা’ রোগে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯৫১-র জানুয়ারি, স্ত্রীর অসুস্থতার খবরে কলকাতা আসেন কবি। লাবণ্যদেবী সুস্থ হচ্ছেন না দেখে ছুটির সময় বৃদ্ধির আবেদন করেন কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ ২৫ ফেব্রুয়ারি তাঁকে বরখাস্ত করে দেয়। এ-সময় সহকর্মী পুলিনবিহারিকে কবি লেখেন, ‘বড়ই বিপদের ভেতর আছি। খড়্গপুর কলেজে থেকে ডিসেম্বর ও জানুয়ারিতে তিনশত টাকা পেয়েছিলাম। ফেব্রুয়ারি মাসে যে কাজ করেছিলাম, সে পাওনা আজ পর্যন্ত পাইনি। অন্তত পূর্বের মাইনে না পেলে এই দুর্দিনে কিছুতেই টিকে থাকতে পারবো না।’ এ-সময় চরম বেকারত্ব। তাঁর কাঁধেই সংসারের ভার। বাড়ি নিয়ে, পরিবার নিয়ে তাঁর শত দুশ্চিন্তা। খড়্গপুরের কলেজের সাড়ে পাঁচ মাসের মেয়াদি চাকরি চলে যাওয়ার পর সম্পূর্ণ বেকারত্ব তাঁকে অসহায় অবস্থার মধ্যে ঠেলে দেয়। শুরু হয় আবার চাকরির খোঁজ। শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেও সন্তুষ্ট ছিলেন না, সম্ভবত নিশ্চিন্ত কোনো শিক্ষকতাও কোনোদিন পাননি। তবু একটা কাজের খোঁজে হন্যে হয়ে উঠেছিলেন, চিঠি লিখেছিলেন শিক্ষকতা/অধ্যাপনা চাকরির খোঁজের জন্য হরপ্রসাদ মিত্র, নরেশ গুহ কিংবা অনিল বিশ্বাসকে। হরপ্রসাদ মিত্রকে লিখেছিলেন, ‘অমৃতবাজার পত্রিকায় দেখা গেছে, কলকাতার কয়েকটি প্রথম শ্রেণির কলেজে ইংরাজি শিক্ষক নেওয়া হবে। কিন্তু কলেজের নামের পরিবর্তে পোষ্ট বক্স নম্বর ব্যবহূত বলে বুঝতে পারছি না স্কটিশচার্চ অথবা সিটি কলেজের প্রয়োজনে এই বিজ্ঞাপন।’ আর্থিক প্রয়োজনে জীবনানন্দ একসময় সিনেমার গান লিখবার কথাও ভেবেছিলেন। বন্ধু কবি অরবিন্দ গুহের কাছে একবার জানতে চেয়েছিলেন— ‘সিনেমার গান লিখলে নাকি টাকা পাওয়া যায়? তুমি কিছু জানো এ বিষয়ে?’ অরবিন্দ বাবু তখন এ বিষয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে যোগাযোগের কথা বলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাছে বিষয়টি তুলতে পারেননি কবি। এরপর অরবিন্দ বাবু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কথা বলেন। সিনেমার ডিরেক্টর শৈলজানন্দ বাবু জীবনানন্দের কাছের মানুষ ছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও আগের মতোই কবি আর বিষয়টি তুলতে পারেননি। কারণটি বেশ মজা করে অরবিন্দবাবুকে তিনি বলেছিলেন। সকৌতুক ভঙ্গিতে তিনি বলেন, ‘যদি শৈলজা আমার জন্য কোথাও একটা ব্যবস্থা করে দেয়, তাহলেও আমি কেমন করে লিখব— ‘রাঁধে-এ-এ-এ, ঝাঁপ দিলি তুঁই মরণ যমুনায়’।” এই কথোপকথনের কিছুদিনের মধ্যেই সেই মহা দুর্ঘটনা, ১৪ অক্টোবর। এমনই একদিন আড্ডার ছলে জীবনানন্দ অরবিন্দ গুহকে বলেছিলেন, ‘আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। আমি মানুষের নীতিবোধে বিশ্বাস করি।’ এই বিশ্বাসের প্রতিফলন ছিলো জীবনানন্দের জীবন ও সাহিত্যে, কবিতায় ও কথায়। গোটা জীবন যে আর্থিক অনিশ্চয়তা তাকে তাড়া করে বেড়িয়েছে, তাই তার প্রধান ছিলো বিপন্নতা। ১৯৫১-তে যে দুর্বিষহ আর্থিক চাপ তাঁর ওপর নেমে আসে তাতে একসময় বিপন্ন জীবনানন্দ জনৈক পরিচিতের সঙ্গে ব্যবসায় নামার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন, যদিও তা শেষ পর্যন্ত ভেঙে যায়। খাঁ খাঁ বেকার সংসারের চাপে জীবনানন্দ প্রত্যহ খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের কলম থেকে বিভিন্ন কাজের খোঁজ নিয়ে আবেদন করতে থাকেন। তাঁর এরকম অসহায় জীবনের, অর্থাৎ কর্মহীন পর্বে একবার পরিচিতদের পরামর্শে দেখা করতে গিয়েছিলেন রাইটার্সে রেভিনিউ বোর্ডের সদ্য আইসিএস সত্যেন ব্যানার্জীর সঙ্গে। দেখা করতে গিয়ে রীতিমতো অসুস্থ হয়ে পড়েন, রাইটার্স বিল্ডিংয়েই অবনীমোহন কুশারীর ঘরে তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন। পরের বছর চাকরি পেলেন তাঁর স্ত্রী লাবণ্য দাশ। এ-সময়ই চার মাসের জন্য চাকরি পান জীবনানন্দ, ১৯৫২-র নভেম্বর থেকে ১৯৫৩-র ফেব্রুয়ারি, বড়িশা কলেজে শিক্ষকতার। কিন্তু এখানেও থাকা হয়নি। এই সময়কালে তিনি এতটাই বিপন্ন ছিলেন যে কবিতাও লিখে উঠতে পারছিলেন না। এ সময়ের একটা ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। সুরজিৎ দাশগুপ্ত একবার ‘জলার্ক’-এর জন্য বুদ্ধদেব বসুর কাছে লেখা চাইতে গেলে তিনি প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত লেখার জন্য পৃথক দর উল্লেখ করেছিলেন। সুরজিৎ দাশগুপ্ত একথা জীবনানন্দকে জানিয়ে তাঁর কোনো দর আছে কি না জানতে চাইলে জীবনানন্দ লেখেন, ‘একটি কবিতার জন্য সম্মানমূল্য আমি সাধারণত ২৫/৩০ টাকা থেকে ৫০ টাকা পর্যন্ত পাই, তোমরা ২০ টাকা দাও। আমি সময় করে ভালভাবে নতুন কবিতা লিখে পাঠাই।’ লেখার জন্য সময় ও সাধনা দরকার, গদ্যের চেয়ে কবিতার বেশি। ২ নভেম্বর ১৯৫১-তে তিনি এই চিঠিটি লেখেন। বিভিন্ন জায়গায় কাজের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরেছেন, বছরের পর বছর অনিশ্চিত জীবনযাপন করতে হয়েছে তাঁকে। খবরের কাগজের দপ্তরে কাজও করেছেন। স্বরাজ-এ প্রায় বেতনহীন অবস্থায় কয়েক মাস কাজ করেছেন, রবিবারের সাময়িকী দেখতেন। এই কাগজের চাকরি ছাড়ার পরেই তীব্র আর্থিক দুরবস্থায় পড়ে বাধ্য হন উপন্যাস লিখতে, রোজগারের জন্য, স্বাভাবিকভাবেই অনেকাংশে তা হয়ে ওঠে আত্মজৈবনিক। নিজস্ব যন্ত্রণা-জটিল জীবনের আলো-আঁধার অনুসৃত সৃজনের পেছনে থেকেছে তার আত্মগত উচ্চারণ।
একসময় যে কবি বুঝেছিলেন ‘এ যুগ অনেক লেখকের, একজনের নয় কয়েকজন কবির যুগ; বিংশ শতাব্দীর সূচনাপর্বের স্বপ্ন দেখা জগৎ, স্বপ্ন দেখানো জগৎ, ক্রমশ শতাব্দীর বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাল্টাচ্ছিলো। প্রকৃতির রূপ-রসে নিমজ্জিত কবিও এই যন্ত্রণার বিবর্তন টের পেয়েছেন। যুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, কালোবাজারি, বেকারত্ব, সমাজ ও রাষ্ট্রকে অস্থির করে তুলেছিলো, পরাধীনতার বেদনা ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা— এই সময়ের সর্বোচ্চ আলোড়ন। শতাব্দীর এই রাক্ষসী বেলায় আর বাস্তবের রক্ততটে জীবনানন্দের আগমন। যার কাছে বাংলার লক্ষ গ্রাম ‘নিরাশায় আলোকহীনতায় ডুবে নিস্তব্ধ নিস্তেজ’। জীবনানন্দ যে যন্ত্রণায় তাড়িত হয়েছিলেন তা কি শুধু বাইরের জগতের, নাকি তাঁর অভ্যন্তরের, খবর কে রাখে? তাঁর যন্ত্রণার চিহ্ন নিয়ে রয়ে গেছে তাঁর কবিতা— ‘কোনোদিন মানুষ ছিলাম না আমি,/হে নর, হে নারী,/তোমাদের পৃথিবীকে চিনিনি কোনদিন;/...গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত;/আমাকে কেন জাগাতে চাও?’
তাঁর ‘আট বছর আগের একদিন’ পর্বের কবিতায় জীবনানন্দের যে আস্তিক্যবোধের স্পর্শ পাই, সংশয়ের চিহ্ন দেখি তা পরবর্তীকালে ‘মহাজিজ্ঞাসা’য় দৃঢ় হয়ে ওঠে। জীবন যাঁর কাছে ছিলো ‘অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থাকা’, সেই তিনিই লেখেন, ‘তবু চারিদিকে রণক্লান্ত কাজের আহ্বান।/সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে এ-পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে;’। জীবনের প্রতি প্রত্যাশামুক্ত কবিকে ক্রমশ মৃত্যুবোধ আচ্ছন্ন করছিলো। স্বেচ্ছা ধ্বংসের যে ধূসর ছায়ায় তিনি বিশ্রাম নিতে চেয়েছিলেন, সেই শান্তি তাকে দিয়েছিলো মৃত্যু, স্বেছা আহূত কি সেই মৃত্যু? যেখানে কবি বলেন, ‘কোনোদিন জাগিবে না আর/জানিবার গাড় বেদনার/ অবিরাম— অবিরাম ভার/সহিব না আর’। ৎ