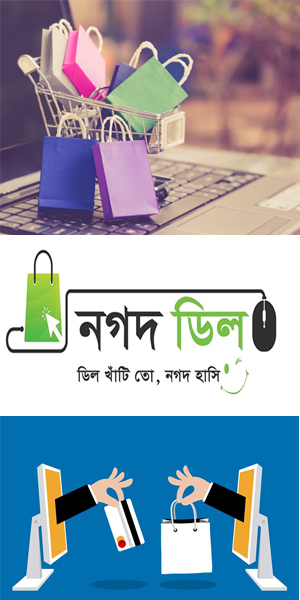প্রায় ২০০ বছরের দাসত্বের পর ব্রিটিশদের কবল থেকে মুক্ত হয়েছিল ভারতীয় উপমহাদেশ। ঔপনিবেশিক শাসনের জাঁতাকল থেকে মুক্তি পেতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা ছিল অনেকটা প্রদীপের সলতের মতো। একদিকে তারা নিজেদের ভবিষ্যতের নিরাপত্তাকে দূরে সরিয়ে বিপ্লবের পথে এগিয়ে দিয়েছিলেন তাদের স্বামী, সন্তান ও ভাইদের। অন্যদিকে তারা কখনো ঘরের ভেতর থেকে কখনো বাইরে বেরিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন। এমনকি হাতে অস্ত্রও তুলে নিয়েছিলেন। স্বাধীন সূর্যোদয়ের জন্য সাধারণ নারী থেকে যারা অগ্নিকন্যারূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত, লীলা নাগ, মনোরমা বসু, ইলা মিত্র অন্যতম। শুধু স্বাধীন সংগ্রাম নয়, যুগে যুগে নারীদের কাছেও তারা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবেন। জেনে নিন, তাদের সংগ্রামী জীবনের কথা-
ইলা মিত্র
১৯৫০ সালের ৭ জানুয়ারি সাঁওতাল বেশ ধারণ করে ভারতে যাওয়ার সময় সীমানা পার হওয়ার প্রস্তুতিকালে রোহনপুর রেলওয়ে স্টেশনে ধরা পড়ে যান। ধরে আনা হয় নাচোল স্টেশনে। পুলিশ শুরু করে অমানুষিক নির্যাতন। কারণ যেভাবেই হোক স্বীকার করাতে হবে পুলিশ কর্মকর্তা ও কনস্টেবল হত্যার পেছনে তার ইন্ধন ও পরিকল্পনা ছিল। টানা চার দিন প্রচণ্ড অত্যাচারের পর নাচোল স্টেশন থেকে তাকে নবাবগঞ্জ পুলিশ স্টেশনে আনা হয়। সে সময় তার শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে রক্ত ঝরছিল, গায়ে ছিল অসহনীয় জ্বর। তবুও তার ওপর নির্যাতন থেমে থাকেনি। তার ওপর যেসব অত্যাচার চালানো হয় তার মধ্যে ছিল- বাঁশকল, শরীরের নাজুক অংশে বুটের আঘাত, অনাহারে রাখা, পায়ের গোড়ালি দিয়ে লোহার পেরেক ঢুকিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। কিন্তু শত অত্যাচারেও তার স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারেনি শাষক শ্রেণি।

তিনি ইলা মিত্র। তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী, বাংলার কৃষকের রানিমা। বাংলার শোষিত ও বঞ্চিত কৃষকের অধিকার আদায়ে যিনি এগিয়ে এসেছিলেন। ভোগ করেছেন অমানুষিক নির্যাতন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সাধারণ মানুষের জন্য লড়ে গেছেন এই সংগ্রামী নারী।
১৯২৫ সালের ১৮ অক্টোবর কলকাতায় জন্মের পর নাম রাখা হয়েছিল ইলা সেন। বাবা নগেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের অধীন বাংলার অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল। তাদের আদি নিবাস ছিল তৎকালীন যশোরের ঝিনাইদহের বাগুটিয়া গ্রামে। কলকাতার বেথুন স্কুল ও কলেজের পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন ইলা মিত্র। ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন রাজ্য জুনিয়র অ্যাথলেটিক্সে চ্যাম্পিয়ন। সাঁতার, বাস্কেটবল ও ব্যাডমিন্টন খেলায়ও ছিলেন পারদর্শী। তিনিই প্রথম বাঙালি মেয়ে যিনি ১৯৪০ সালে জাপানে অনুষ্ঠিতব্য অলিম্পিকের জন্য নির্বাচিত হন। খেলাধুলা ছাড়াও গান, অভিনয়সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী।
নারী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বেথুন কলেজে থাকাবস্থায়ই রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন ইলা। ১৯৪৩ সালে রাওবিল বা হিন্দু কোড বিলের বিরুদ্ধে মহিলা সমিতির সক্রিয় সদস্য হিসেবে আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তিনি। আন্দোলনের কাজ করতে গিয়ে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৪৫ সালে বিয়ে করেন কমিউনিস্ট রমেন্দ্র মিত্রকে। রমেন্দ্র ছিলেন মালদহের নবাবগঞ্জ থানার রামচন্দ্রপুর হাটের জমিদার মহিমচন্দ্র ও বিশ্বমায়া মিত্রের ছোট ছেলে। বিয়ের পর ইলা সেন হলেন জমিদার পুত্রবধূ ইলা মিত্র। রক্ষণশীল জমিদার পরিবারের নিয়মে অন্দরমহলেই থাকতেন তিনি। এই বন্দিজীবনে মুক্তির স্বাদ নিয়ে এলো বাড়ির কাছেই মেয়েদের জন্য একটি স্কুল। গ্রামে সবার দাবি, নিরক্ষর মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর দায়িত্ব নিতে হবে বধূমাতা ইলাকে। মাত্র তিনজন ছাত্রী নিয়ে স্কুলটি শুরু হলেও ইলার আন্তরিক পরিচালনায় তিনমাসে ছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৫০-এ। এভাবেই অন্দর থেকে আবারো বাইরে বের হয়ে আসেন তিনি।
এ সময় স্বামী রমেন্দ্রর কাছে জমিদার ও জোতদারের হাতে বাংলার চাষিদের নিদারুণ বঞ্চনা শোষণের কাহিনী শুনতেন তিনি। রমেন্দ্র এর আগেই জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করতে নিজের পরিবারকে ত্যাগ করে কৃষকের পাশে দাঁড়িয়েছেন। স্বামীর আদর্শ ও পথ চলার সঙ্গে সহজেই নিজেকে যুক্ত করেছিলেন ইলা। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত রাজশাহীর নবাবগঞ্জ অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করেন ইলা মিত্র। আন্দোলনের মাঝপথে একমাত্র পুত্রসন্তানের জন্ম হলে গোপনে তাকে শাশুড়ির কাছে রেখে ফিরে এসেছিলেন কৃষকের মধ্যে।
বাংলার গ্রামীণ সমাজে ব্রিটিশ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত ভূমির মালিক ছিলেন চাষিরা। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলনের ফলে চাষিদের জমির মালিকানা চলে যায় জমিদারদের হাতে। মধ্যস্বত্বভোগী এক শ্রেণির উদ্ভব ঘটে; যারা কৃষকের জমি চাষ তদারকি ও খাজনা আদায় করত। ফসল উৎপাদনের খরচ কৃষকরা বহন করলেও উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক তুলে দিতে হতো জোতদারদের হাতে। এ ব্যবস্থাকে বলা হতো ‘আধিয়ারী’।
নাচোলে কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন ইলা ও রমেন্দ্র মিত্র। ১৯৫০ সালের ৫ জানুয়ারি পুলিশের একজন কর্মকর্তাসহ একদল কনস্টেবল নাচোলের চণ্ডীপুর গ্রামে এলে তাদের ঘেরাও করে বিক্ষোভ করতে থাকে গ্রামবাসী। এক পর্যায়ে উন্মত্ত গ্রামবাসী ওই পুলিশ কর্মকর্তা ও পাঁচ পুলিশ কনস্টেবলকে হত্যা করে। দু’দিন পর ৭ জানুয়ারি শুরু হয় পুলিশের প্রতিশোধ। তারা বারোটি গ্রাম ঘেরাও করে, ঘরবাড়ি ধ্বংস করে, চারদিকে গুলি চালিয়ে হত্যা করে অনেক গ্রামবাসীকে। তীর-ধনুকে সজ্জিত সাঁওতাল, হিন্দু ও মুসলিম কৃষকদের বেশিক্ষণ টিকতে না পেরে পিছপা হয়ে যে যেদিক পারলেন গা-ঢাকা দেয়। রমেন্দ্র মিত্র পালিয়ে ভারতে চলে যান। কিন্তু গ্রেফতার হন ইলা মিত্র।
সরকারের পক্ষ থেকে ইলা, রমেন্দ্র মিত্র ও মাতলা মাঝি নামে এক সাঁওতাল নেতাকে প্রধান আসামি করে পুলিশ হত্যা মামলা দায়ের করা হয়। কোনো প্রত্যক্ষ সাক্ষী ও আলামত না পাওয়া সত্ত্বেও তাদের তিনজনের যাবজ্জীবন শাস্তির রায় হয়। ইলাকে রাজশাহী জেলে প্রেরণ করা হয়। পুলিশের নির্যাতনে তখন ইলা মিত্রের শারীরিক অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। ১৯৫৩ সালে তাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তর করা হয়। ইলা মিত্র ও তার সহযোদ্ধারা তখন ছাত্র-জনতার চোখে অত্যন্ত সম্মানের পাত্র। সাধারণ মানুষ মুক্তির দাবি তোলে। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এলে মুখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের উদ্যোগে ইলা মিত্রকে বিদেশে চিকিৎসার জন্য প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়।
কলকাতা মেডিকেল কলেজে দীর্ঘ আটমাস চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। একমাত্র পুত্র রণেন মিত্র মোহনের মুখ দেখেন দীর্ঘ ছয় বছর পর। শোষিত জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় মাতৃত্বকে ত্যাগের এই দৃষ্টান্ত সত্যিই বিরল।
সুস্থ হয়ে তিনি কলকাতা সিটি কলেজে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করে ১৯৮৯ সালে অবসর নেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি পশ্চিম বঙ্গের সব গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও সংগঠনের জন্য কাজ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গেও বিভিন্ন আন্দোলনের জন্য ১৯৬২, ১৯৭০, ১৯৭১ ও ১৯৭২ সালে কারাবরণ করেছেন। বাংলাদেশের মানুষের জন্য তার ছিল বিশেষ আন্তরিকতা। মুক্তিযুদ্ধে তিনি বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য অক্লান্তভাবে কাজ করেছেন।
উপমহাদেশের নারী জাগরণ ও কৃষক আন্দোলনের এই কিংবদন্তি নেত্রী ৭৭ বছর বয়সে ২০০২ সালের ১৩ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন।
কল্পনা দত্ত
বীর কন্যা কল্পনা দত্ত ১৯১৩ সালের ২৭ জুলাই চট্টগ্রামের বোয়ালখালী থানার খরণদ্বীপ ইউনিয়নের শ্রীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা বিনোদ বিহারী দত্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের সাব রেজিস্ট্রার হওয়ায় কল্পনার শৈশব কাটে চট্টগ্রাম শহরে। শহরের প্রাণকেন্দ্র আন্দরকিল্লায় তাদের বিশাল বাড়ি ছিল। শহরের নামকরা ডাক্তার রায় বাহাদুর দুর্গাদাস দত্ত ছিলেন তার দাদু।
কল্পনা দত্তের পড়াশোনার হাতেখড়ি পরিবারে। প্রাথমিক লেখাপড়া শেষে তাকে ডা. খাস্তগীর স্কুলে ভর্তি করে দেন তার বাবা। বীরকন্যা প্রীতিলতাও এই স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। কল্পনা দত্ত প্রীতিলতার এক ক্লাস নিচে পড়তেন। স্কুলের শিক্ষিকা ঊষাদি ছাত্রীদেরকে দেশ-বিদেশের গল্প শোনাতেন। কল্পনা দত্ত এই ঊষাদির সংস্পর্শে এসেই বিভিন্ন স্বদেশী বই পড়তে শুরু করেন। ঊষাদি ছিলেন স্বদেশীদের গোপন বিপ্লবী সহযোগী। তিনিই মূলত কল্পনা দত্তের চেতনায় দেশপ্রেম ও বিপ্লবী রাজনীতির বীজমন্ত্র বুনে দেন।

১৯২৯ সালে মেট্রিক পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অর্জন করেছিলেন তিনি। ভালো ফল করার জন্য সরকার তাকে ১৫ টাকা বৃত্তি প্রদান করে। ওই বছরই তিনি আইএসসিতে কলকাতার বেথুন কলেজে ভর্তি হন। বেথুন কলেজে ভর্তির কয়েক দিন পর প্রীতিলতার সঙ্গে তার যোগসূত্র তৈরি হয়। প্রীতিলতা ওই একই কলেজে ইংরেজি সাহিত্যে বিএ পড়ার পাশাপাশি মাস্টারদার নির্দেশে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছিলেন। তার গড়ে তোলা বিপ্লবী চক্রের সঙ্গে যুক্ত হন কল্পনা। চক্রের মূল কাজই ছিল বিপ্লবীকর্মী তৈরির পাশাপাশি অর্থ সংগ্রহ। এ সময় দেশের মুক্তি সংগ্রাম, মাতৃভূমির স্বাধীনতা, নারীদের মর্যাদা রক্ষার জন্য বীর সন্তানদের আত্মত্যাগ ভাবিয়ে তোলে কল্পনা দত্তকে। এভাবে ধীরে ধীরে তিনি নিজেই বিপ্লবীকর্মী হয়ে যান। মেয়েদের বিপ্লবে অংশগ্রহণের অনুমতি চাওয়ার জন্য দেখা করতে চান সর্বাধিনায়ক সূর্যসেনের সঙ্গে।
১৯২৯ সালের শেষের দিকে পূজার ছুটিতে কতকগুলো বোমার খোল নিয়ে প্রীতিলতা, কল্পনা দত্ত, সরোজিনি পাল, নলিনী পাল, কুমুদিনী রবিত চট্টগ্রাম আসেন। মাস্টারদার নির্দেশে তারা খোলগুলো পৌঁছে দেন বিপ্লবীদের হাতে। ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল করেন।
মে মাসের প্রথম দিকে বিপ্লবে অংশ নিতে প্রীতিলতা ও কল্পনা দত্ত কলকাতা থেকে চট্টগ্রামে এসে আত্মগোপনে থাকা মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করেন এবং সশস্ত্র বিপ্লবে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হওয়ার প্রতিজ্ঞা করেন। এ সময় কল্পনা দত্ত চট্টগ্রাম কলেজে বিএসসিতে ভর্তি হন। পড়াশোনার ফাঁকে গোপনে চলতে থাকে বিপ্লবী কার্যক্রম।
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল, জালালাবাদ সম্মুখ সমর, কালারপোল, ফেনী, ঢাকা, কুমিল্লা, চন্দননগর ও ধলঘাটের বীরোচিত সংগ্রামের অধ্যায়গুলো মুক্তিকামী বিদ্রোহীদের নতুন প্রেরণা জুগিয়েছিল। ওই দিনগুলোতে এক দিন পুরুষের বেশে কল্পনা তার আন্দরকিল্লার বাসা থেকে গোপন বিপ্লবী কেন্দ্র কাট্টলী যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন। কিন্তু পথে পাহাড়তলি স্টেশনের কাছেই কিছু বখাটের সহায়তায় পুলিশের হাতে ধরা পড়েন তিনি। শুরু হয় রাজনৈতিক কারাজীবন। ১৯৩১ সালের মে মাসে ছাড়া পাওয়ার পর কলকাতা থেকে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক দ্রব্য কৌশলে নিয়ে আসার দায়িত্ব পান। ডিনামাইট ফিউজ দিয়ে চট্টগ্রাম আদালত ভবন ও কারাগার উড়িয়ে দিয়ে বিচারাধীন বিপ্লবীদের মুক্ত করার পরিকল্পনা ছিল তার।
১৯৩১ সালের এপ্রিল মাসে এক বিশেষ আদালতে শুরু হয় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল মামলায় অভিযুক্ত ৩২ বন্দির বিচার। মাস্টারদা মাইন ব্যবহার করে জেলের প্রাচীর উড়িয়ে দিয়ে বন্দিদের মুক্ত করা এবং একই সঙ্গে আদালত ভবন ধ্বংস করার উদ্যোগ নেন। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন কল্পনা। হামলার দিন একেবারে শেষ মুহূর্তে সর্বশেষ মাইনটি বসানোর সময় পুলিশের নজরে পড়ে যাওয়ায় গোটা পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। এ ঘটনায় পুলিশ কল্পনাকে সন্দেহভাজন রূপে তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কড়া নজরদারির মধ্যেও কল্পনা দত্ত প্রায়ই গভীর রাতে সূর্য সেন, নির্মল সেন প্রমুখ নেতার সঙ্গে দেখা করতে তাদের গোপন আস্তানায় যেতেন এবং বিপ্লবী কাজের প্রশিক্ষণ নিতেন। ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণে প্রীতিলতার সঙ্গে যৌথ নেতৃত্ব দেওয়ার কথা ছিল তার। কিন্তু তার পূর্বেই পুরুষের ছদ্মবেশে সহকর্মী নির্মল সেনের সঙ্গে মাস্টারদার কাছে দেখা করতে যাওয়ার সময় পুলিশ কল্পনা দত্তকে গ্রেফতার করে। দুই মাস জেলে থাকার পর প্রমাণাভাবে তিনি জামিনে মুক্ত হন। ১৯৩২ সালে বিপ্লবী প্রীতিলতা ও কল্পনাকে ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের ভার দেওয়া হয়। কিন্তু দুর্ঘটনাবশত ১৯৩২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর আবারো ধরা পড়ে যান কল্পনা। জামিনে মুক্তির পর পাহাড়ে আত্মগোপন করেন কল্পনা। ১৯৩৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি সমুদ্রতীরবর্তী গৈরালা গ্রামে ইংরেজ ফৌজের সঙ্গে সংঘর্ষে মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদারের সঙ্গী ছিলেন তিনি। পরে মাস্টারদা ও ব্রজেন সেন পুলিশের হাতে ধরা পড়লেও কল্পনা পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। কিন্তু তিন মাস পর ১৯ মে গৈরালা গ্রামে এক সশস্ত্র সংঘর্ষের পর কল্পনা কয়েকজন বিপ্লবীসহ ধরা পড়েন।
ওই বছর ১৪ আগস্ট একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল সূর্যসেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারকে ফাঁসি দেয় এবং অন্যদেরকে আন্দামান সেলুলার জেলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল মামলার দ্বিতীয় বিচার পর্বে কল্পনা দত্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ৬ বছর কারাভোগের পর তিনি কারামুক্ত হন। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন তিনি। ১৯৪০ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পুলিশ তাকে স্বগৃহে অন্তরীণ রাখে। এরপর তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশ নেন।
দেশ ভাগ হওয়ার পরও অনেক দিন তিনি চট্টগ্রামেই থেকে যান। ১৯৫০ সালে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটে চাকরি নেন এবং পরবর্তী সময়ে দিল্লিতে বসবাস শুরু করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর আমন্ত্রণে অন্যান্য বিপ্লবী কমরেডদের সঙ্গে কল্পনা দত্ত চট্টগ্রামে আসেন। ১৯৯৫ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি এই বীরকন্যা মৃত্যুবরণ করেন।
লীলা নাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী, পূর্ব বাংলার নারীশিক্ষা ও নারী আন্দোলনের পথিকৃৎ লীলা নাগ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন নেত্রী। ১৯০০ সালের ২১ অক্টোবরের আসামে গোয়ালপাড়ায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে সম্মান ও স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তার শিক্ষাগত সাফল্যের জন্য তাকে ‘পদ্মাবতী’ স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। বাবার বদলি সূত্রে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯২৩ সালে ইংরেজিতে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন।

লীলা নাগ একজন বিপ্লবী ও আন্দোলনকারী। ছাত্রাবস্থায় তিনি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের ব্যাপারে জনমত গড়ে তুলতে নিখিল বঙ্গ নারী ভোটাধিকার সমিতির যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে নারীশিক্ষা প্রসারের মূল উদ্দেশ্য নিয়ে দীপালি সঙ্ঘ নামে নারীদের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। দীপালি সঙ্ঘের সাহায্য নিয়ে দীপালি স্কুল নামে একটি স্কুল ও অন্য বারোটি ফ্রি প্রাইমারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নারীশিক্ষা মন্দির ও শিক্ষাভবন নামে পরিচিত অন্য দুটি স্কুলও প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমান নারীদের শিক্ষায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।
ঢাকায় তার প্রতিষ্ঠিত একটি স্কুল (দীপালি-১) পরবর্তীকালে কামরুন্নেসা গার্লস স্কুল হিসেবে পরিচিত হয়।
১৯২৫ সালে শ্রীসঙ্ঘ নামে অভিহিত একটি বিপ্লবী দলের সদস্য হন তিনি। ছাত্রীদের জন্য তিনি ঢাকাভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং আসাম ও বাংলার অনেক স্থানে এর শাখা প্রসারিত করেন। ছাত্রীদের সুবিধার জন্য তিনি কলকাতায় একটি মহিলা হোস্টেল প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকায় গোপন বিপ্লবী দলের সদস্য হিসেবে লীলা তাদের সাহায্য করতেন এবং এ দলসমূহ ও বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের, বিশেষত নারী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সংযোগকারী হিসেবে কাজ করতেন। প্রীতিলতার মতো সুপরিচিত নারী বিপ্লবীদের প্রেরণার উৎস হিসেবে তিনি প্রভাব রেখেছেন।
১৯২৭-২৮ সালের বিক্ষুব্ধ বছরগুলোতে, যখন নারীরা শারীরিক আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত হয়, তখন লীলা নাগ মহিলা আত্মরক্ষা ফান্ড নামে একটি ফান্ড গঠন করেন, যা ছিল এ অঞ্চলে প্রথম মার্শাল পদ্ধতিতে আত্মরক্ষামূলক দলের একটি। সাধারণ জনতার পর্যায়ে নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি গণশিক্ষা পরিষদ নামে পরিচিত একটি প্রতিষ্ঠানও গঠন করেন।
লীলা অন্য যে কারণে বিখ্যাত তা হলো নারীবিষয়ক প্রভাবশালী সাময়িক পত্রিকা জয়শ্রীর সম্পাদক হিসেবে তার সাহিত্যিক কার্যক্রম। নারীদের দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত এ সাময়িক পত্রিকাটি নারী-কর্তৃক লিখিত নিবন্ধাবলি প্রকাশ করত। লবণ সত্যাগ্রহের একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে লীলা ঢাকা মহিলা সত্যাগ্রহ কমিটি গঠন করেন। শ্রীসঙ্ঘের প্রধান অনিল রায়ের গ্রেফতারের পর এ সংগঠনটির পরিচালনার দায়িত্ব লীলার ওপর দেওয়া হয়। ১৯৩১ সালের ২০ ডিসেম্বর তাকে গ্রেফতার করে বিনাবিচারে কারাগারে পাঠানো হয়।
১৯৩৯ সালে লীলা নাগ অনিল রায়কে বিয়ে করেন। এই দম্পতি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর দলে যোগদান করে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করেন। ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে কলকাতার হলওয়েল মনুমেন্টের বাহ্যিক আকৃতি নষ্ট করার দায়ে লীলা নাগ ও অনিল রায়কে অভিযুক্ত করা হয় এবং আবার তাদের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তারা কারাগারে আটক থাকেন। কারামুক্তির পর তাকে নেতাজীর দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র ফরওয়ার্ড ব্লকের সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়। পরবর্তী সময়ে তিনি পশ্চিম বাংলায় চলে যান এবং ভারতীয় জাতীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪৬ সালে তিনি বাংলা থেকে ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং ভারতীয় শাসনতন্ত্রের খসড়া তৈরিতে অবদান রাখেন। ১৯৪৬ সালের কলকাতা দাঙ্গা ও নোয়াখালী দাঙ্গার পর তিনি নোয়াখালীতে দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের ত্রাণকার্যে অংশগ্রহণ করেন। ‘ন্যাশনাল সার্ভিস ইনস্টিটিউট’ নামক একটি জনকল্যাণমূলক সংগঠনও তিনি স্থাপন করেন। ১৯৭০ সালের ১১ জুন এই মহীয়সী নারীর জীবনাবসান ঘটে।
রাসিমণি হাজং
রাসিমণি হাজং বা রশিমণি হাজং ১৯৪৬ সালে সংঘটিত ময়মনসিংহের টঙ্ক আন্দোলনের অন্যতম বিপ্লবী নেত্রী। তিনি এ আন্দোলনের প্রথম শহীদ। টঙ্ক আন্দোলনের বিপ্লবী নেতা মণি সিংহের পরই রাসিমণি হাজং এবং কুমুদিনী হাজংয়ের অবদানের কথা স্মরণ করা হয়। নেত্রকোনা জেলায় রাসিমণি হাজংয়ের স্মরণে নির্মিত একটি স্মৃতিসৌধ রয়েছে।
১৯০১ সালে রাসিমণি হাজং বর্তমান নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর উপজেলাধীন কুল্লাগড়া ইউনিয়নের বহেরাতলি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
রাসিমণি হাজং টঙ্ক প্রথা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেন। তিনি ছিলেন কৃষক সমিতির বিপ্লবী সদস্য। ১৯৪৬ সালে ভিয়েতনাম দিবস উপলক্ষে ময়মনসিংহ শহরে মিছিলের ওপর গুলিবর্ষণের ফলে একজন ছাত্র নিহত হয়। সেজন্য সমগ্র ময়মনসিংহ জেলায় তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় বহেরাতলী গ্রামে পুলিশের হানায় ত্রাসের সৃষ্টি হয়। পুলিশ সে গ্রামের কুমুদিনী ওরফে সরস্বতী নামে এক যুবতী নারীকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। গ্রামের কৃষক সমিতির কর্মীরা তখন দুর্গাপুরের জনসভা থেকে ফিরছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন মহিলা কর্মী রাসিমণি। তিনি অসহায় কুমুদিনীকে উদ্ধারের সঙ্কল্পে হাতে থাকা দা দিয়ে পুলিশকে কোপাতে শুরু করেন। তখন পুলিশ গুলি চালায়। গুলিতে রাসিমণি এবং সুরেন্দ্রনাথ নামে অপর এক কর্মী মারা যান। এই খবর পেয়ে কৃষকরা পুলিশ বাহিনীকে ঘিরে আক্রমণ শুরু করে। সংঘর্ষে দুই পুলিশ মারা যায় ও অন্যরা পালিয়ে যায়।

জানা যায়, হাজং এলাকায় কৃষক বিদ্রোহ দমনকারী মিলিটারিদের হাত থেকে কৃষক বধূ সরস্বতীকে বাঁচাতে গিয়ে দা’র কোপে এক সৈন্যের দেহ মাথা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন রাসিমণি। সোমেশ্বরী নদীর ধারে এই হাজং বিদ্রোহে শঙ্খমণি, রেবতী, নীলমণি, পদ্মমণিসহ অনেকে শহীদ হন। বহেরাতলী গ্রামের সেই ঘটনার সরেজমিনে তদন্ত করতে জ্যোতি বসু, ব্যারিস্টার স্নেহাংশুকান্ত আচার্য গারো পাহাড় অঞ্চলের হাজং অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ময়মনসিংহের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ব্যাস্টিন তাদের বহেরাতলী গ্রামে প্রবেশ করতে দেননি।
মনোরমা বসু
উপমহাদেশের ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, নারীমুক্তি আন্দোলন, মুক্তি সংগ্রামের অনন্য পথিকৃৎ মনোরমা বসু। ভারতবর্ষজুড়ে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন চলার সময় যখন স্বদেশিরা রাস্তায় গান গেয়ে মিছিল নিয়ে যাচ্ছিল তখন সেই মিছিলেই হাতে হলুদ রাখি বেঁধে স্বদেশি আন্দোলনে দীক্ষা নেন তিনি। ১৯৩০ সালে চৌদ্দ বছর বয়সে বরিশালের বাঁকাই গ্রামের জমিদার চিন্তাহরণ বসুর সঙ্গে তার বিবাহ হয় এবং স্বামীর প্রত্যক্ষ সমর্থনে তিনি স্বদেশি আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। বরিশালে অবস্থানকালে মনোরমা স্বদেশি আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং নারী অধিকার রক্ষায় ‘সরোজনলিনী মহিলা সমিতি’র শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশে এটিই ছিল প্রথম মহিলা সংগঠন। এ সমিতির মাধ্যমেই তিনি নারী সমাজকে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেন। ১৯৩০ সালে ভারতজুড়ে যখন চলছিল আইন অমান্য আন্দোলন। এ আন্দোলনে মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে এবং জীবনে প্রথমবারের মতো তিনি কারাবন্দি হন। শাস্তি হিসেবে ৬ মাস জেল ও ১৫০ টাকা জরিমানা ধার্য করা হয়। জেলে থাকাকালীন তিনি ঊর্মিলা দেবী (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বোন), জ্যোতির্ময়ী দেবী প্রমুখ প্রখ্যাত কংগ্রেস নেত্রীর সান্নিধ্য লাভ করেন।

মনোরমা বসু ছিলেন একজন একনিষ্ঠ সমাজসেবক। তিনি অনাথ ও দুস্থ মহিলাদের, বিশেষ করে বিধবা ও কুমারী মেয়েদের আশ্রয়দানের জন্য বরিশালের কাউনিয়ায় ‘মাতৃমন্দির আশ্রম’ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ‘মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি’র বরিশাল জেলা শাখার অন্যতম নেত্রী ছিলেন। ১৯৪৩-৪৪ সালে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সময় লঙ্গরখানা, চিকিৎসালয় ও উদ্ধার আশ্রম স্থাপন এবং পুনর্বাসন কাজে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া বরিশাল জেলার বিভিন্ন নারী আন্দোলন, সমাজসেবা ও রাজনৈতিক কাজের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ‘বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, বরিশাল জেলা শাখা’ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি নারীমুক্তি আন্দোলনকে গতিশীল করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ পরিষদের সহসভানেত্রী ছিলেন।
১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর নতুন শাসকদের শাসন ও শোষণ জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৮ সালে বরিশালের খাদ্য-আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে তিনি এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন এবং সেই সঙ্গে জননিরাপত্তা আইনে আরো তিন বছর কারাভোগের পর ১৯৫২ সালের ২৫ এপ্রিল মুক্তি লাভ করেন। ১৯৫৪ সালে তদানীন্তন পূর্ব বাংলায় রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিলে মনোরমা বসু আত্মগোপন করেন এবং সে অবস্থা থেকে আত্মপ্রকাশের পর তিনি ‘মাতৃমন্দির আশ্রম’-এর কাজে নিজেকে পুরোপুরি নিয়োজিত করেন। একই সঙ্গে গড়ে তোলেন আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়, পল্লীকল্যাণ অমৃত পাঠাগার (শহীদ অমৃতলালের নামে), আর শিশুদের জন্য মুকুল মিলন খেলাঘর। তার অবর্তমানে মাতৃমন্দিরের কার্যনির্বাহের জন্য নিজের সব সম্পত্তি মন্দিরের নামে দান করে যান। ১৯৬২ ও ৬৪’র গণআন্দোলন এবং ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে মহিলাদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামেও তার অগ্রণী ভূমিকা ছিল। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মনোরমা বসু প্রথমে দেশেই আত্মগোপন করে থাকেন। পরে জুন মাসে চলে যান ভারতে। সেখানে গিয়েও তিনি মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে প্রচারণা, অর্থ সংগ্রহ, নারীদের সংঘটিত করা ইত্যাদি কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। দেশ স্বাধীন হলে জানুয়ারি মাসেই তিনি দেশে ফিরে আসেন। দেশ পুনর্গঠনের কাজে নিয়োজিত হন। মহিলা পরিষদের উদ্যোগে বয়স্কা মহিলাদের জন্য কালীবাড়ি রোডের চণ্ডীসদনে স্থাপন করেন বৈকালিক স্কুল।
১৫ আগস্টের পর রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন এবং অস্থিরতার জন্য পার্টির সিদ্ধান্তে আত্মগোপন করেন। সে অবস্থাতেও দেশপ্রেম, সমাজসেবা ও মানুষের প্রতি ভালোবাসার কারণে দলমত-নির্বিশেষে সবাই তাকে ‘মাসিমা’ বলে ডাকত। বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী, দৃঢ়চেতা, পরোপকারী এবং আদর্শনিষ্ঠ মনোরমা বসুর সমগ্র জীবন ছিল দেশপ্রেমে নিবেদিত। তিনি ছিলেন সাম্যবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত এবং যেকোনো সামাজিক ও রাজনৈতিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠ। মহীয়সী এই নারীর জন্ম ১৮৯৭ সালে এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৯৮৬ সালের ১৬ অক্টোবর।
প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার
প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ছিলেন ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে প্রথম শহীদ বিপ্লবী বাঙালি নারী। তিনি জন্মেছিলেন চট্টগ্রামের ধলঘাট গ্রামে। জন্ম ৫ মে, ১৯১১ সাল, মৃত্যু ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩২। দেশমাতার মুক্তির জন্য মাত্র ১৯ বছর বয়সে তিনি আত্মহুতি দেন। মাস্টারদা সূর্যসেনের ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। তারই নির্দেশে তিনি চট্টগ্রামের পাহাড়তলীর ইউরোপিয়ান ক্লাবে দলবল নিয়ে আক্রমণ করতে যান। আক্রমণ ব্যর্থ হয়ে গেলে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে তিনি পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন।
ইউরোপিয়ান ক্লাবে তখন ইংরেজ অফিসাররা সন্ধ্যাবেলা বসে আড্ডা দিত, পানভোজন করত, গানবাজনাও হতো। বাইরে সাইনবোর্ডে লেখা ছিল- কুকুর ও ভারতীয়দের জন্য প্রবেশ নিষিদ্ধ। মাস্টারদা অনেক দিন থেকেই ভাবছিলেন এ ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করবেন। ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের সিদ্ধান্ত প্রথমবার নেওয়া হয়েছিল ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল। গুড ফ্রাইডের কারণে সেদিনের আক্রমণ করা যায়নি। তারপর আক্রমণের চূড়ান্ত দিন ঠিক হয় ১৯৩২-এর ১০ আগস্ট। শৈলেশ্বর চক্রবর্তীর নেতৃত্বে সাতজনের একটা দল সেদিন ক্লাব আক্রমণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। শৈলেশ্বর চক্রবর্তীর প্রতিজ্ঞা ছিল ক্লাব আক্রমণের কাজ শেষ হওয়ার পর নিরাপদ আশ্রয়ে ফেরার যদি সুযোগ থাকে তবুও তিনি আত্মবিসর্জন দেবেন। তিনি পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন। গভীর রাতে কাট্টলীর সমুদ্রসৈকতে তার মৃতদেহ সমাহিত করা হয়। মাস্টারদা এরপর ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ক্লাবে হামলা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই আক্রমণের দায়িত্ব তিনি নারী বিপ্লবীদের ওপর দেবেন বলেন মনস্থির করেছিলেন। কিন্তু সাতদিন আগেই পুলিশের হাতে পুরুষবেশী কল্পনা দত্ত ধরা পড়ে গেলে আক্রমণে নেতৃত্বের ভার পড়ে একমাত্র নারী বিপ্লবী প্রীতিলতার ওপর। ২৩ সেপ্টেম্বর এ আক্রমণে প্রীতিলতার পরনে ছিল মালকোঁচা দেওয়া ধুতি আর পাঞ্জাবি, চুল ঢাকার জন্য মাথায় সাদা পাগড়ি, পায়ে রবার সোলের জুতা, ইউরোপীয় ক্লাবের পাশেই ছিল পাঞ্জাবিদের কোয়ার্টার। এর পাশ দিয়ে যেতে হবে বলেই প্রীতিলতাকে পাঞ্জাবি ছেলেদের মতো পোশাক পরানো হয়েছিল।

সেদিন ছিল শনিবার, প্রায় চল্লিশজন মানুষ তখন ক্লাবঘরে অবস্থান করছিল। ক্লাবের ভিতর থেকে রাত আনুমানিক ১০টা ৪৫ মিনিটে আক্রমণের নিশানা দেখানোর পরই ক্লাব আক্রমণ শুরু হয়। তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে বিপ্লবীরা ক্লাব আক্রমণ করে। পূর্বদিকের গেট দিয়ে ওয়েবলি রিভলভার এবং বোমা নিয়ে আক্রমণের দায়িত্বে ছিলেন প্রীতিলতা, শান্তি চক্রবর্তী আর কালীকিংকর দে। প্রীতিলতা হুঁইসেল বাজিয়ে আক্রমণ শুরুর নির্দেশ দেওয়ার পরই ঘন ঘন গুলি আর বোমার আঘাতে পুরো ক্লাব কেঁপে কেঁপে উঠছিল। ক্লাবঘরের সব বাতি নিভে যাওয়ার কারণে সবাই অন্ধকারে ছুটোছুটি করতে লাগল। ক্লাবে কয়েকজন ইংরেজ অফিসারের কাছে রিভলভার ছিল। তারা পাল্টা আক্রমণ করল। একজন মিলিটারি অফিসারের রিভলভারের গুলিতে প্রীতিলতার বাঁ-পাশে আঘাত লাগে। প্রীতিলতার নির্দেশে আক্রমণ শেষ হলে বিপ্লবী দলটার সঙ্গে তিনি কিছুদূর এগিয়ে আসেন। পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী সেদিনের এই আক্রমণে মিসেস সুলিভান নামে একজন নিহত হন এবং চারজন পুরুষ এবং সাতজন মহিলা আহত হন।
পাহাড়তলী ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণ শেষে পূর্বসিদদ্ধান্ত অনুযয়ী প্রীতিলতা পটাশিয়াম সায়ানাইড মুখে পুরে দেন। কালীকিংকর দে’র কাছে তিনি তার রিভলভারটা দিয়ে আরো পটাশিয়াম সায়ানাইড চাইলে, কালীকিংকর তা প্রীতিলতার মুখের মধ্যে ঢেলে দেন। পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়া প্রীতিলতাকে বিপ্লবী শ্রদ্ধা জানিয়ে সবাই স্থান ত্যাগ করে। পরদিন ক্লাব থেকে ১০০ গজ দূরে মৃতদেহ দেখে প্রীতিলতাকে শনাক্ত করে পুলিশ। তার মৃতদেহ তল্লাশির পর বিপ্লবী লিফলেট, অপারেশনের পরিকল্পনা, বিভলভারের গুলি, রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ছবি এবং একটা হুঁইসেল পাওয়া যায়। ময়নাতদন্তের পর জানা যায় গুলির আঘাত তেমন গুরুতর ছিল না এবং পটাশিয়াম সায়ানাইড ছিল তার মৃত্যুর কারণ।