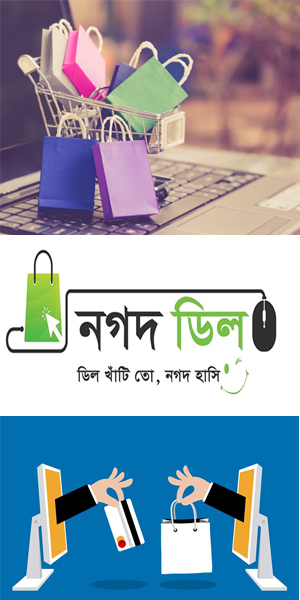মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎসব হচ্ছে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা। সারা বিশ্বে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে অত্যন্ত জাঁকজমক ও ধুমধামের সঙ্গে এই ধর্মীয় দিবস দুটি পালিত হতে দেখা যায়। বাংলাদেশে এখন যেভাবে ঈদ উৎসব পালিত হচ্ছে, একশ বছর আগেও কী এভাবে হতো? সাধারণ মানুষ কি আজকের মতো অধীর আগ্রহ, উৎসাহ নিয়ে তাকিয়ে থাকতেন ঈদের চাঁদের দিকে? ঈদের ধুমধামের দিকে? ইতিহাস বলে ‘না’। তবে সে আমলে কীভাবে বাংলাদেশে ঈদ উৎসব পালিত হতো?
রমজান মাস মুসলমানদের সবচেয়ে পবিত্র মাস এবং কোরআনে একমাত্র এ মাসের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। এ মাসেই নাজিল হয়েছে কোরআন শরিফ। প্রথম ওহী পেয়েছিলেন হজরত মোহাম্মদ (সা.)। গিয়েছিলেন তিনি মিরাজে। মক্কা থেকে মদিনায় যাওয়ার আগে রমজানের সঙ্গে পরিচয় ছিল না। মুসলমানদের এর সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল হিজরতের পরেই। রমজান শব্দটি এসেছে আরবি ‘রমজা’ ধাতু থেকে। রমজান মানে দাহ, তাপ বা পোড়ানো। চন্দ্রবর্ষই নিয়ন্ত্রণ করে মুসলমানদের উৎসব। অনেক আগে প্রাচীনকালে গরমের মৌসুমে এই মাস পড়ত বলে এর নাম হয় রমজান। রমজানের সঙ্গে উপবাসের প্রতি শব্দের ধ্বনিগত কোনো মিল নেই। উপবাসের আরবি নাম হচ্ছে ‘সওম’। এর অর্থের সঙ্গে উপবাস ব্রতের কোনো মিল নেই। এর আভিধানিক অর্থই হলো আরাম বা বিশ্রামে থাকা। রমজান শেষে ঈদুল ফিতর। ঈদের অর্থ হলো উৎসব এবং আভিধানিক অর্থ হলো বার বার ফিরে আসা। ঈদ শব্দটি মূলত সিরিয়ার। ঈদ শব্দটির আদি অর্থ ও তার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম নিরীক্ষণ করে দেখে মনে হয়, হয়তো এককালে এ ধরনের এক সামাজিক উৎসবের সঙ্গে পরিচিত ছিল সিরিয়ার দামেস্কের অধিবাসীরা। হয়তো সিরিয়ার দামেস্কের কৃষিজ আচার অনুষ্ঠানের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত ছিল এই আজকের ঈদ উৎসব এবং তাদের কাছ থেকেই আচার অনুষ্ঠান জ্ঞাপক শব্দের মতোই আরবরা আমদানি করেছেন বর্তমান এই ঈদ উৎসব ও তার প্রকৃতিকে। ইসলাম প্রচারের শুরুতে অর্থাৎ আদি বাঙালি মুসলমানরা কীিভাবে ঈদ উৎসব পালন করত তা রীতিমতো গবেষণার বস্তু। তবে বলা যেতে পারে, আদিতে প্রচার করা আরবের উদযাপিত ঈদের আদি রূপই হয়তো তুলো ধরেছিলেন। কিন্তু কালের গর্ভে সময়ের বিবর্তনে সে রূপ চিরতরে হারিয়ে গেছে।
উৎসব হিসেবে বাংলাদেশের মানুষ শতবর্ষ আগে ঈদের দিনটি কীভাবে পালন করতেন, সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে মানুষের মনেও পরিবর্তন ঘটেছে। ধীরে ধীরে সাংস্কৃতিক বিবর্তন সংঘটিত হয়েছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের ফলে। এখানে পুরনো আমল বলতে আমরা আশি-নব্বই বছরের বাংলাদেশের চিত্র তুলে ধরতে চাই। শতবর্ষ আগে সাহিত্য, সংবাদ সাময়িকী পত্রে ঈদের তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য বিবরণ আমরা পাইনি। এদেশের হিন্দু, মুসলমান যিনিই আত্মজীবনী লিখে গেছেন তাদের রচনায় আমরা দুর্গাপূজা, জন্মাষ্টমী, মহররম এমনকি রথযাত্রা, দোল পূর্ণিমা, দিপালী উৎসব- এ ধরনের বিভিন্ন পূজা-পার্বণ সম্পর্কে বিস্তর উল্লেখ দেখতে পাই। শুধু পাওয়া যায় না ঈদুল ফিতর সম্পর্কে। তবে একালে যারা জন্মেছিল, তাদের বিবরণীতে কচিৎ ঈদুল ফিতর সম্পর্কে খানিকটা তথ্য পাওয়া যায়। এতে প্রমাণিত হয় ঈদুল ফিতরের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ উৎসব শতবর্ষ আগেও বাঙালির ঘরে ঘরে আজকার মতো অনাবিল হাসি, আনন্দের বার্তা বয়ে আনতে পারেনি। এ থেকে যদি আমরা বলি ঈদুল ফিতর সেকালে বাংলাদেশে তেমন কোনো বড় উৎসব হিসেবে পালন হয়নি তবে কি তা ভুল বলা হবে? মনে হয় নিশ্চয়ই না। আজ আমরা যে ঈদের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকি, বাঙালির ঈদকে দেখি একটা সামাজিক ধর্মীয় বড় উৎসব হিসেবে তা কিন্তু সত্তর-আশি বছরের ঐতিহ্য মাত্র। বর্তমানে গ্রামবাংলায় রোজা ও ঈদ যেভাবে পালিত হচ্ছে তা কিন্তু সে আমলে অর্থাৎ সত্তর-আশি বছর আগেও এভাবে পালিত হতো না।
শাসক ইংরেজরা স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানদের ঈদকে গুরুত্ব দেয়নি। এজন্য সরকারি ছুটিও বরাদ্দ ছিল কম। তাছাড়া মুসলমানদের পক্ষে ঈদকে সে আমলে উৎসবে পরিণত করা সম্ভব ছিল না। কারণ গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ মুসলমান ছিল বিত্তহীন ও নিরক্ষর। বরং মুসলমানের মহররমের, বিশেষ করে তাজিয়ার বর্ণনা পাওয়া যায় বিস্তর জায়গায় ও সংবাদপত্রে। এটি সে সময় ঢাকায় বেশ জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে পালিত হতো। ঈদ মুসলমানদের প্রধান উৎসব হিসেবে পালিত না হওয়ার আরেকটি প্রধান কারণ ছিল বিশুদ্ধ ইসলাম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা। ফরায়েজি আন্দোলনের আগে (১৮১৮ খ্রি.) গ্রামাঞ্চলে মুসলমানদের কোনো ধারণা ছিল না বিশুদ্ধ ইসলাম সম্পর্কে। ইসলাম ধর্মে লোকজ উপাদানের আধিপত্য ছিল প্রায় ক্ষেত্রেই হিন্দু রীতিনীতির ওপর। ১৮৮৫ সালে জেমস ওয়াইজ তার ‘Notes on the Races castos and trades Eastern Bengal London’ বইতে লিখেছেন, ‘বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সরল অজ্ঞ কৃষক। ঢাকার অদূরে নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে ঈদের দিনে গ্রামবাসীরা জমায়েত হয়েছেন ঈদের নামাজ পড়বেন বলে; কিন্তু সে সময়ে দুর্ভাগ্য এই যে, জামাতের একজনও জানতেন না কীভাবে ঈদের নামাজ পড়তে হয়। পরবর্তীকালে ঢাকায় নৌকাযোগে এক যুবক যাচ্ছিলেন। তাকেই ধরে নিয়ে এসে পড়ানো হয়েছিল ঈদের নামাজ।’ ঐতিহাসিক মুনতাসীর মামুন উল্লেখ করেছেন, তার পিতার সহকর্মী যিনি ছিলেন সে আমলে একজন নামজাদা পীর, তাকে বলেছিলেন, মুসলমান ছিলাম বটে [তার জন্ম ১৮৯৮ সালে] কিন্তু ছেলেবেলায় রোজা বা ঈদ সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণা ছিল না। মসজিদ ছিল হয়তো কয়েক গ্রাম মিলে একটি। সে সময় বাংলা ‘মাসিক সঞ্জীবনা’ পত্রিকার সম্পাদক (কৃষ্ণ কুমার মিত্র) লিখেছিলেন, [উনিশ শতকের মাঝামাঝি ময়মনসিংহের গ্রামাঞ্চলের মুসলমানদের সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন] ‘সে সময় মুসলমানরা নামাজ পড়িত না। গ্রামে কোনো মসজিদ ছিল না। স্থানে স্থানে দরগা ছিল।
এবার ভিন্ন প্রসঙ্গে আসা যাক। সেকালে ঢাকায় রমজানের চাঁদ দেখার জন্য বিকাল থেকেই বড় কাটরা, আহসান মঞ্জিল, হোসনি দালানের ছাদে ভিড় জমে উঠত। চাঁদ দেখামাত্রই পরস্পর সালাম বিনিময় এবং সেই সঙ্গে গোলাবাজি ও তোপের আওয়াজে সারা ঢাকা শহর প্রকম্পিত ও মুখরিত হয়ে উঠত। ঢাকার রমজান ও ঈদের বড় আকর্ষণ ছিল রকমারি খাবার। নিজের ঘরে পর্যাপ্ত ইফতারি থাকা সত্ত্বেও সবাই একবার ‘চকে’ ছুটে যেতেন। চকবাজার সেই মোগল আমল থেকেই তার ঈদের আভিজাত্য বজায় রেখেছে। চকবাজার সেই আমল থেকেই ব্যবসা-বাণিজ্য এবং খাবার-দাবার ও আড্ডার মুখ্য কেন্দ্রস্থল ছিল। ‘চকে’ সে আমলের রকমারি ইফতারি খাবারের মধ্যে বিখ্যাত ছিল শিরমাল, বাকরখানি, রুটি, চাপাতি, নানরুটি, কাকচা, নানখাদাই, শিক কাবাব, হান্ডি কাবাব, মাছ ও মাংসের কোপ্তা, সামি কাবাব, টিকিয়া কাবাব, পরোটা, বোগদাদি রুটি, শরবতি রুটি ও মোরগ কাবাব, ফালুদার শরবত, জাফরান শরবত, বেলের শরবত ও নানারকম ফল। ‘চক’ এখনো রোজার সময় প্রায় সেই পুরনো ঐতিহ্য বজায় রেখেছে।
মোগল আমলে ঈদের দিন যে হৈ চৈ ও বর্ণাঢ্য আনন্দ উৎসব পালিত হতো, তা বহিরাগত উচ্চ পদধারী বা ধনাঢ্য মুসলমানদের মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ। এসবের সঙ্গে সাধারণ গ্রামবাংলার মানুষের ছিল যোজনব্যাপী ব্যবধান। আর সে আমলে ধনাঢ্য মুসলমান ব্যক্তিরা পথে প্রচুর পরিমাণ টাকাকড়ি ছড়িয়ে দিতেন, গরিবদের কাছে কিছু দান-খয়রাতও করতেন এমন তথ্য সে আমলে বিদ্যমান রয়েছে। মোগলরা যে ঈদের গুরুত্ব দিতেন তা বোঝা যায় বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় শাহী ঈদগাহের ধ্বংসাবশেষ দেখে। এরকম একটি ঈদগাহ এখনো বিদ্যমান রয়েছে ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায়, শাহ সুজা যখন বাংলার সুবাদার তখন তার প্রধান আমাত্য মীর আবুল কাসেম ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করেছিলেন এই ঈদগাটি।
এ শতকের তৃতীয় চতুর্থ দশকের গ্রামাঞ্চলে ঈদ পালনের কয়েকটি বর্ণনা পাই খন্দকার আবু তালিবের নিবন্ধ থেকে- “রোজার পনেরো দিন যাওয়ার পর থেকেই গৃহবধূরা নানা রকম নিশ পিঠা তৈরি করতে শুরু করতো। এদের মধ্যে ফুল পিঠা, পাপর পিঠা, ঝুরি, হাতে টেপা সেমাই ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। শবেকদরের রাতে মেয়েরা মেহেদী এনে তা বেটে হাতে নানা রকম চিত্র আঁকতো। ফুল পিঠা তৈরি করার সময় বউয়েরা ‘প্রিয় স্বামী’, আর অবিবাহিত মেয়েরা ‘বিবাহ’ ও ‘প্রজাপতি’ এঁকে রাখতো। ঈদের দিনে যুবক-যুবতী, বন্ধু-বান্ধবীদের পাতে দেয়ার জন্যেই এ ধরনের ফুল পিঠা তৈরি করা হতো।”
সেকালের বাংলার রোজা ও ঈদ একালে এখন অবশ্যই ভিন্নতর রূপ পেয়েছে। বছর ঘুরে আসে, গ্রামে রোজা, রমজান মাস, গ্রামবাংলার মানুষের কাছে পরম বিশ্বাস চাঁদ দেখে রোজা শুরু, চাঁদ ওঠা দেখে রোজার শেষ। চাঁদই তাদের লক্ষ্যস্থল। রমজানের ঈদে চাঁদ দেখার জন্য একালে পাড়ায় পাড়ায় ধুম পড়ে যায়। পবিত্র ঈদের চাঁদ দেখে তারা সালাম করে। সালাম করে বাড়ির গুরুজনদের। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগেও আমরা গ্রামবাংলার এই রূপ স্বচক্ষে রমজান মাসে দেখেছি।
বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ আগেও যেমন বঞ্চিত ছিলেন ঈদের আনন্দ থেকে, এখনো বঞ্চিত আছেন তদ্রূপ, প্রতিনিয়ত। মোগল আমলের ইতিহাসে আমরা দেখেছি বিত্তবানরা ঈদের দিন ছুড়ে দিচ্ছেন রেজগি পয়সা আর সাধারণ, নিরন্ন, বঞ্চিত মানুষ তা কুড়িয়ে নিচ্ছেন কাড়াকাড়ি করে। এখনো তার কোনো হেরফের হয়নি বরং বঞ্চনা আরো বেড়েছে। আমরা চোখের সামনে দেখেছি বাংলাদেশে ধনীর গৃহে জাকাতের কাপড় নেওয়ার জন্য ছিন্নমূল মানুষের হুটোপুটি লাইন। তা আমাদের হতভাগ্য, বঞ্চিত, দরিদ্র, নিপীড়িত মানুষের চেহারাই তুলে ধরে। সুতরাং ঈদুল ফিতরের আনন্দ সাধারণ মানুষের মনে আজ আর কোনোই রেখাপাত করে না।
লেখক : অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা