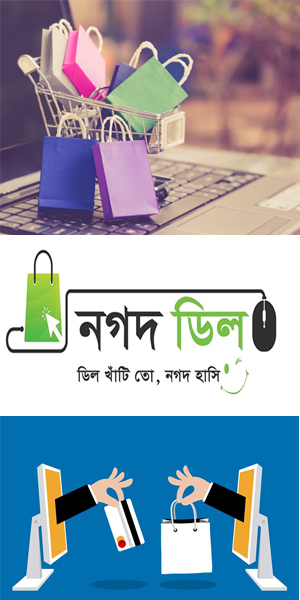এস এম জাহাঙ্গীর আলম সরকার পিপিএম
স্বাধীন সার্বভৌম প্রতিটি রাষ্ট্রের যেমন একটি জাতীয় পতাকা রয়েছে, তেমনি প্রত্যেকের আছে নিজস্ব সংস্কৃতি থেকে উৎসারিত জাতীয় সংগীত। বিশ্ব দরবারের যে কোনো বৃহত্তর কনফারেন্স কিংবা খেলাধুলার মতো বড় আসরে যে দুটি বিষয় সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের পরিচয় বহন করে, তার একটি জাতীয় পতাকা, অন্যটি হলো জাতীয় সংগীত। দুটি বিষয় যতটা না ধর্মের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক সংস্কৃতির সঙ্গে। কারণ একটি দেশের জাতিসত্তার সঙ্গে তার সংস্কৃতি যত বেশি সম্পৃক্ত, পৃথকভাবে ধর্মীয় অনুভূতির সম্পৃক্ততা এত বেশি পরিলক্ষিত হয় না কোনো দেশের জাতীয় সংগীত পর্যালোচনা করলে। অন্তর্নিহিত বড় একটি কারণও রয়েছে। তা হলো, একটি দেশের সংস্কৃতি একাধিক ধর্মকে আশ্রয় দিতে পারে। ফলে সব ধর্মই সংস্কৃতিতে আশ্রিত হয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা রূপলাভ করে অসাম্প্রদায়িক চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। ফলে একটি দেশে একাধিক ধর্মের মানুষ একই রকম অধিকার নিয়ে, সুযোগ-সুবিধা নিয়ে, নাগরিকত্ব নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করতে পারে। বিশ্বে এমন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কল্পনা করা সত্যিই কঠিন, যেখানে শুধু একটি ধর্মের মানুষ বাস করে। একটি দেশে অধিক সংখ্যক নাগরিক একটি বিশেষ ধর্মের অনুসারী হতে পারে। কিন্তু তার সামগ্রিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন একশভাগ মানুষ একই ধর্মে বাস করে এমন অস্তিত্ব বিশ্বে আছে বলে আমার জানা নেই। সংস্কৃতির এত বড় ক্যানভাসের মতো অন্তর্নিহিত মূল্যে ধর্মের ক্যানভাস এত বড় থাকলেও দৃশ্যমান বাস্তবতায় একটি ধর্ম তার নিজস্ব অস্তিত্বের আমিত্ব প্রকাশ করতে গিয়েই অন্য ধর্মকে আশ্রয় দেওয়ার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সেটি নিজের পরিপূরক হিসেবে কখনো দিতে সক্ষম হয় না। এটি বড়মাপের একটি সীমাবদ্ধতা। রাষ্ট্রীয় আচার অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীতের গুরুত্ব এতটা ব্যাপৃত হলেও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, আসমানি কিংবা সনাতন ধর্মে রাষ্ট্র পরিচালনায় জাতীয় সংগীতের বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা আছে বলে আমার জানা নেই। একই ধর্মের মানুষ বিশ্বের নানা রাষ্ট্রে বসবাস করে থাকে। কাজেই ধর্মে যদি জাতীয় সংগীতের বিষয়টি উল্লেখ থাকত, তাহলে ধর্মমতের সেই মানুষগুলো বিশ্বের যেখানেই বাস করুক না কেন, তারা সেটি পাঠ করতে পারত। আবার এই বিষয়কে কেন্দ্র করে নানারকম দ্বন্দ্ব বিশৃঙ্খলাও দেখা দিত নিঃসন্দেহে। কাজেই ধরেই নেওয়া যায় জাতীয় সংগীত বিষয়টি মূলত ধর্মীয় সংস্কৃতির অংশ নয়।
একটি দেশের জাতীয় মূল্যবোধ তথা জাতিসত্তা এবং সে দেশের অভ্যন্তরে বিদ্যমান সামগ্রিক সংস্কৃতির চেতনা থেকে উৎসারিত হয় সে দেশের জাতীয় সংগীত। দেশপ্রেমের নিবিড় সম্পর্ক থাকায় একটি দেশে একাধিক জাতিসত্তার অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হলেও সবাই মিলে জাতীয় সংগীতকে সমভাবে সম্মান করতে শেখে। সংস্কৃতির ধর্মীয় অংশে দেশপ্রেমের প্রতি সব ধর্মই অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। যেমন ইসলাম ধর্মমতে দেশপ্রেমের মধ্যে ঈমানকে অঙ্গীভূত করা হয়েছে। আর ঈমান হলো এই ধর্মমতের মানুষের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি আবশ্যকতা। যা না থাকলে এ ধর্মমতের মানুষ হিসাবে সে পরিপূর্ণ নয়। জাতীয় সংগীতকে কটাক্ষ করা, বিদ্রূপ করা কিংবা সমালোচনার ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠ অনুভূতির স্খলন হলে স্ব-স্ব ধর্মের আদর্শ থেকে বিচ্যুতি ঘটতে পারে এ বিষয়টি ভেবে দেখার যুক্তিসঙ্গত গুরুত্ব রয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।
বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের উপজীব্য উপকরণগুলো বিশ্লেষণ করলে রবিঠাকুরের কল্পচিত্রে নিখাদ দেশপ্রেম, মা-মাটি-মানুষ, ঋতুবৈচিত্র্য, প্রকৃতির আকাশ-বাতাস থেকে শুরু করে নানারকম সুন্দরের সমাবেশ সন্নিবেশিত হয়ে বাংলার অপরূপ সৌন্দর্যের মহিমা প্রকাশ পেয়েছে। যার সৃষ্টিকাল ১৯০৫ সালে। শব্দচয়ন ও ভাষাশৈলীর কোথাও বিন্দুমাত্র সাম্প্রদায়িকতার কোনো গন্ধ নেই। প্রকৃতির এমন শোভা ও সৌন্দর্য প্রকাশ এবং বাংলা সংস্কৃতির অনন্য উপস্থাপনে আর কোনো বাংলা গান খুব একটা পাওয়া যায় না। কাছাকাছি অনুভূতিকে নাড়া দিয়ে যায় আরেকটি গান যেমন রয়েছে তা হলো দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ‘ধনধান্য পুষ্পভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা’। আমরা অনেকেই জানি না, আমাদের জাতির পিতার অন্তরে এ দুটি গান কত বেশি সমাদৃত ছিল। তিনি নিজে যেমন গুনগুন করে গাইতেন, তেমনি সুযোগ পেলেই চেতনা নির্মাণের মন্ত্র হিসেবে শিল্পীদের এই গানটি পরিবেশনে অনুপ্রাণিত করতেন। তার এই চেতনার প্রকাশ মেলে বাংলাদেশ জন্মেরও বহু আগে। মূলত তার চিন্তা, চেতনা ও দর্শনের সঙ্গে একাকার হয়ে যে সময়কাল বা দিনক্ষণটিতে ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি’ এই গানটি মিশে একাত্ম হয়ে গেছে, ঠিক সেই দিনেই আমাদের জাতীয় সংগীতের উন্মেষ ঘটেছে। যদিও তা বাংলাদেশ-উত্তর আনুষ্ঠানিক জাতীয় সংগীত ঘোষণার অনেক আগের ঘটনা। এ প্রসঙ্গে জাতির পিতার স্ব-প্রণোদিত উচ্চারণ ছিল “এই সঞ্চয়িতা সঙ্গে থাকলে আমি আর কিছুই চাই না। নাটক নয়, উপন্যাস নয়, কবিগুরুর গান ও কবিতাই আমার বেশি প্রিয়। সব মিলিয়ে এগারো বছর কাটিয়েছি জেলে। আমার সব সময়ের সঙ্গী ছিল এই সঞ্চয়িতা। কবিতার পর কবিতা পড়তাম আর মুখস্থ করতাম। এখনো ভুলে যাইনি। এই প্রথম মিয়ানওয়ালি জেলের নয় মাস সঞ্চয়িতা সঙ্গে ছিল না। বড় কষ্ট পেয়েছি। আমার একটি প্রিয় গানকেই ‘আমার সোনার বাংলা’ আমি স্বাধীন দেশের জাতীয় সংগীত করেছি। আর হ্যাঁ, আমার আরেকটি প্রিয় গান ডি এল রায়ের ‘ধনধান্য পুষ্পভরা’। দুটি গানই আমি কাজের ফাঁকে গুনগুন করে গেয়ে থাকি।”
স্মরণ রাখা দরকার, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়কালীন বাস্তবতায় এই গানটি নতুন ব্যঞ্জনা নিয়ে প্রতিভাত হয়েছিল সব যোদ্ধার প্রাণে প্রাণে। সাহসী ও অনুপ্রাণিত করেছিল যুদ্ধের ময়দানে অংশগ্রহণকারী, আত্মদানকারী সব মুক্তিযোদ্ধাকে। শক্তি, চেতনা ও অনুপ্রেরণার ক্ষেত্রে লোকজ বাউল সুরের এই গানটি বাংলা ও বাঙালির জীবনে সমসাময়িক হয়ে একই রকম আবেদন নিয়ে প্রাণসঞ্চার করেছে। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের অতীত প্রেক্ষাপটেও। আমাদের জাতীয় সংগীতের মূল বিশেষত্ব ঠিক এখানেই— যে কোনো প্রয়োজনে অসীম শক্তিমত্তা প্রদর্শনপূর্বক সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখার যুদ্ধে তার অসীম তেজদীপ্ততা।
যুগে যুগে রবীন্দ্রবিদ্বেষী ছিল, আছে, থাকবে। তাদের কাছে এখন শুনতে হয় কেন রবীন্দ্রসংগীত এদেশের জাতীয় সংগীত হবে? জাতীয় সংগীত নিয়ে নানারকম বিদ্রূপাত্মক কথাবার্তা, অসংলগ্ন সাম্প্রদায়িক বক্তব্য তারা দীর্ঘকাল দিয়ে আসছে। একটু পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, এই শ্রেণির মানুষের এমন মানসিকতা সেই পাকিস্তানি মনস্তত্ত্ব থেকে উৎসারিত ও উচ্চারিত হয়েছে। শুধু জাতীয় সংগীত নয়, তাদের মনস্তত্ত্বে বাংলার যেকোনো সংগীত তথা বাঙালির চেতনা উৎসারিত মূল সংস্কৃতির সবটুকুই অপছন্দের। বলে রাখা দরকার, বাংলা সংস্কৃতি এতটাই ঋদ্ধ যে, কারো অপছন্দতে এ সংস্কৃতির কিছু যায় আসে না।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদীয়মান তেজোদীপ্ত রাজনীতিকে তথা বাংলাদেশের জন্মস্বপ্নকে ধূলিসাৎ করার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসাহিত্যকে নিষিদ্ধ করার বিষয়কে কূটকৌশল হিসেবে গ্রহণ করে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। জাতির পিতা বিষয়টি অনুধাবন করে ১ জানুয়ারি ১৯৭১-এ আরেকটি ভাষণে বলেন, ‘বাংলা ভাষা ও বঙ্গ সংহতিকে ধ্বংস করার জন্যে জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরো স্থাপন করা হয়েছে। পাকিস্তান বেতার এবং টেলিভিশনও এই ষড়যন্ত্রের দোসর। তারা রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধ করে দিয়েছিল এবং আজো এ ব্যাপারে উঁচু মহলে জোর আপত্তি রয়েছে। জনগণ তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এই চক্রান্ত সহ্য করবে না। বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে যেসব বাঙালি সরকারি সমর্থন পেয়েছেন, তাদের দিন আজ শেষ।’ শুধু তা-ই নয়, সাম্প্রদায়িক এ মন্ত্রে বাংলার মানুষ যারা দীক্ষিত হবে তারা বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক চেতনা থেকে দূরে সরে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধেই অবস্থান নেবে, এটাই তাদের কূটকৌশলের অন্তর্নিহিত লক্ষ্য ছিল। যার বাস্তব উদাহরণ আমরা দেখতে পাই পাকিস্তানি কারাগারে বঙ্গবন্ধুকে রবীন্দ্রনাথের ‘সঞ্চয়িতা’ বইটি সঙ্গী হিসেবে অনুমোদন না দিয়ে তা রেখে দেওয়া হয়।
বাংলা ভাষার জাদুকরি শক্তি এবং মার্গীয় উচ্চতা বিশ্বব্যাপী সেদিনই অনুভব করে, যখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ সালে ভাষা সাহিত্যে নোবেল পেলেন। সম্ভবত পাকিস্তানি বুদ্ধিজীবীরা এবং পাকিস্তানি শাসকশ্রেণি তখন থেকেই বাংলা ভাষার গলা টিপে ধরার সংকল্প শুরু করে, যার চূড়ান্ত রূপ প্রদর্শিত হয় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে। সে প্রেক্ষাপট সবারই জানা। এরপরই বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে জেল-জুলুম-অত্যাচার অব্যাহত রেখে বঙ্গবন্ধুর অপ্রতিরোধ্য গতিকে আটকে দেওয়ার লক্ষ্যে নতুন কূটকৌশলের অংশ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ তথা রবীন্দ্রসাহিত্যকে নিষিদ্ধ করার অপপ্রয়াস চালানো হয়। বাংলাদেশের এক শ্রেণির মানুষ পাকিস্তানি শাসকশ্রেণির মানসিকতার সঙ্গে একমত পোষণ করে বাংলাদেশ জন্মের বিরোধিতা করেছে এবং এই শ্রেণির মানুষের বেশিরভাগই ছিল তথাকথিত ধর্মাশ্রয়ী মানুষ। তাদেরকে আরো বেশি সোচ্চার করার লক্ষ্যে হিন্দু কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য অনুশীলনকে তাদের ধর্মীয় রীতির বিপরীতে দাঁড় করিয়ে বাংলাদেশের এই শ্রেণির মানুষের মগজ ধোলাই করেছিলেন বেশ শক্ত করেই। যদিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিখাদ হিন্দু বলার সুযোগ নেই, কেননা তিনি পারিবারিকভাবেই ব্রাহ্ম্য ধর্মাবলম্বী ছিলেন, ধর্মবিশ্বাস মতে যা একেশ্বরবাদী। পাকিস্তানি মস্তিষ্কজাত ঠিক সেই মানসিকতার পরম্পরা বাংলাদেশের একটি বিশেষ শ্রেণি গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে এখনো বিদ্যমান রয়েছে। যার ফলে আমরা দেখতে পাই আমাদের জাতীয় সংগীত নিয়ে তাদের নানারকম কটাক্ষ, বিদ্রূপাত্মক ব্যবহার এবং ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ। মূলত বাংলা সংস্কৃতিকেই তারা বিজাতীয় সংস্কৃতি বলে ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে চলেছেন আজো।
ধর্মনিরপেক্ষতার মন্ত্রে দীক্ষিত অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে বিনষ্ট করে, সাধারণ মানুষকে সার্বক্ষণিক সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনা দ্বারা পরিচালিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যারা বিশ্বাস করে না, ওইসব পাকিস্তানি ভাবধারার মানুষগুলো নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের মনে রাখা দরকার ধর্মকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ লেগে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়নি বরং নানারকম জুলুম-অত্যাচার, শোষণ-বঞ্চনা, গঞ্জনার মতো অধর্ম থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে অনিবার্য কারণে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। এটি মোটেও ধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের যুদ্ধ ছিল না। বাঙালি সংস্কৃতিকে গলা টিপে ধ্বংস করে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে পাকিস্তানের সংস্কৃতিকে পরিপূর্ণরূপে চালু করার যে অপচেষ্টা যুগ যুগ ধরে তারা চালিয়েছিল তা রুখে দিয়ে বাংলা ভাষা, বাঙালি সংস্কৃতিকে বাংলার একান্ত সম্পদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জন্ম দেন। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অত্যাচার, শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে যতটা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির লক্ষ্য অন্তর্নিহিত ছিল, একই ধারায় সাংস্কৃতিক মুক্তির চেতনাও সমভাবে নিহিত ছিল।
লেখক : পুলিশ সুপার ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব