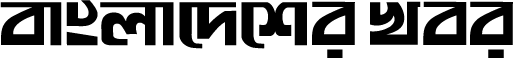খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় নাঙ্গলকোটে ইফতার ও দোয়া
নাঙ্গলকোট (কুমিল্লা) প্রতিনিধি
প্রকাশ: ১৫ মার্চ ২০২৫, ২৩:০০
-67d5b2101ce83.jpg)
কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার বটতলী ইউনিয়নে বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার (১৪ মার্চ) বটতলী ইউনিয়ন বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের আয়োজনে বটতলী আব্দুল মতিন উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বটতলী ইউনিয়ন বিএনপির নেতা ও সমাজসেবক আতাউর রহমান খান।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন বিএনপির নেতা কায়কোবাদ, প্রফেসর আফজালুর রহমান, যুবদল নেতা ওমর ফারুক সবুজ, মেম্বার জাকির হোসেন, সাবেক মেম্বার আলাউদ্দিন, মীর আহম্মেদ মিঠু, সোহাগ খান, বটতলী ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক আহ্বায়ক ইস্রাফিল সুমন, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক সুমন রানা, ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক সদস্য নাজমুল হাসান ও ছাত্রদল নেতা আলম হাসানসহ অন্যরা।
অনুষ্ঠানে সার্বিক সহযোগিতা করেন উপজেলা যুবদলের সদস্য ও ঢাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ইয়াছিন হাজারী।