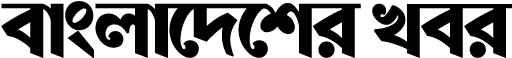প্রতিশ্রুতি ও পরিকল্পনার পরও থমকে গেছে ব্যাংক খাতের সংস্কার
প্রকাশ: ১৩ জুলাই ২০২৫, ১৪:০৬

বাংলাদেশে ব্যাংক খাত সংস্কারের বহু আলোচিত উদ্যোগ নানা প্রতিশ্রুতি ও পরিকল্পনা সত্ত্বেও কার্যত থমকে আছে। অন্তর্বর্তী সরকারের কিছু প্রশাসনিক পদক্ষেপ থাকলেও রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতি, স্বল্পমেয়াদি সরকারের সীমাবদ্ধতা এবং প্রতিষ্ঠানগত দুর্বলতা সংস্কারের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর সম্প্রতি জানান, ‘রিক্স-বেইজড সুপারভিশন’ (আরবিএস) বা ঝুঁকিনির্ভর তদারকি পদ্ধতি ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে পুরোপুরি কার্যকর করার পরিকল্পনা রয়েছে। এখন পর্যন্ত ২০টি ব্যাংকে পাইলটিং সম্পন্ন হয়েছে, বাকিগুলোর কাজ আগামী ছয় মাসে শেষ হবে।
গভর্নরের মতে, ব্যাংক নির্বাহীদের মধ্যেও এ পদ্ধতির ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে। তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, ‘রাজনৈতিক সদিচ্ছা না থাকলে এসব সংস্কার কার্যকর রাখা সম্ভব হবে না।’
অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ জানান, ‘আমরা কিছু মৌলিক সংস্কার হাতে নিয়েছি, যেগুলো ডিসেম্বরের মধ্যেই শেষ করতে পারব। তবে বড় ধরনের কাঠামোগত সংস্কার একটি নির্বাচিত সরকারের মাধ্যমেই সম্ভব।’
তিনি বলেন, ‘দুর্বল ব্যাংকগুলোকে ৭২ হাজার কোটি টাকা তারল্য সহায়তা দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে সঞ্চয়পত্রে মুনাফার হার কমিয়ে আনা হয়েছে, যাতে মানুষ ব্যাংকের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে না ফেলে।’
ড. সালেহ আরও বলেন, ‘পুনর্গঠনের জন্য প্রত্যেক ব্যাংকের সম্পদ ও দায় বিবেচনায় নিতে হবে। এজন্য সময় লাগবে। তবে যাই হোক, আমানতকারীদের টাকা ফেরত দিতেই হবে—এ বিষয়ে কোনো আপস করা যাবে না।’
সংস্কারের চ্যালেঞ্জ ও বাস্তবতা
বিশ্লেষকদের মতে, ব্যাংক খাত সংস্কার যতটা প্রযুক্তিগত বা আর্থিক, তার চেয়ে অনেক বেশি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল।
বিআইবিএম-এর এক গবেষণায় দেখা গেছে, অন্তত ১২টি ব্যাংক ধারাবাহিকভাবে মূলধন ঘাটতির মুখে রয়েছে। এসব ব্যাংক টিকে আছে মূলত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সহায়তায় এবং প্রশাসনিক ছাড়ের মাধ্যমে।
বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন, এই অবস্থা চলতে থাকলে সাধারণ মানুষের আস্থা নষ্ট হবে এবং বাজারে দীর্ঘমেয়াদি তারল্য সংকট সৃষ্টি হতে পারে।
রাজনীতির ভূমিকা
ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, ‘রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছাড়া ব্যাংক খাতের কাঠামোগত সংস্কার সম্ভব নয়।’
আগের বিভিন্ন সরকারে পুনঃতদন্ত, খেলাপি ঋণ পর্যালোচনা, করপোরেট সুশাসন ইত্যাদি নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও বাস্তবায়নের অভাবই বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে থেকেছে।
অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন, নির্বাচনের পর গঠিত একটি রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী ও দায়বদ্ধ সরকার ছাড়া গভীর সংস্কার সম্ভব নয়। কারণ, দুর্বল ব্যাংকের একীভূতকরণ বা লাইসেন্স বাতিলের মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে রাজনৈতিক সাহস প্রয়োজন।
ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা
পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গবেষক ড. আশিকুর রহমান শান্ত বলেন, ‘নতুন গভর্নর দায়িত্ব নেওয়ার পর ব্যাংক খাত থেকে মানি লন্ডারিং ও ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বোর্ড পুনর্গঠন, ইসলামী ব্যাংকে নেতৃত্ব বদল, মুদ্রানীতির কড়াকড়ি এবং ‘ব্যাংকিং রেজোলিউশন অর্ডিন্যান্স’ অনুমোদন—এসব ইতিবাচক পদক্ষেপ।’
এই অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে সরকার এখন প্রয়োজনে ব্যাংকের মালিকানা পুনর্গঠন করতে পারবে। অর্থাৎ, আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষা করেই ব্যর্থ পরিচালকদের মালিকানা বাতিল করা সম্ভব হবে।
তবে মার্জারের প্রক্রিয়া এখনও বড় চ্যালেঞ্জ। ড. আশিকুর রহমান বলেন, ‘বাংলাদেশে ব্যাংক একীভূতকরণের কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। তাই বিদেশি প্রযুক্তিগত সহায়তা নিয়ে এগোতে হবে। এটি ছয় মাস বা এক বছরের প্রকল্প নয়—একটি দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি প্রয়োজন।’
চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভের রিসার্চ ফেলো এম হেলাল আহমেদ জনি বলেন, ‘সংস্কারের কিছু সুফল ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে—যেমন আইনগত কাঠামো শক্তিশালীকরণ, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, তদারকি বাড়ানো এবং তারল্য সহায়তা।’
তবে তিনি বলেন, ‘খেলাপি ঋণ হ্রাস, ব্যাংক বোর্ড পুনর্গঠন এবং দুর্বল ব্যাংক একীভূতকরণে এখনো বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। ঝুঁকিভিত্তিক তদারকি চালু হলে ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতাগুলো আরও স্পষ্ট হবে।’
সংস্কারের গতি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক জটিলতায় থমকে গেছে। নির্বাচনের পর একটি শক্তিশালী সরকার গঠনের মধ্য দিয়েই কেবল বড় ধরনের কাঠামোগত সংস্কার সম্ভব হবে।
এতদিনে ব্যাংক খাত কতটা চাপে পড়বে—এটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।
এএইচএস/এমএইচএস