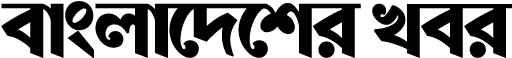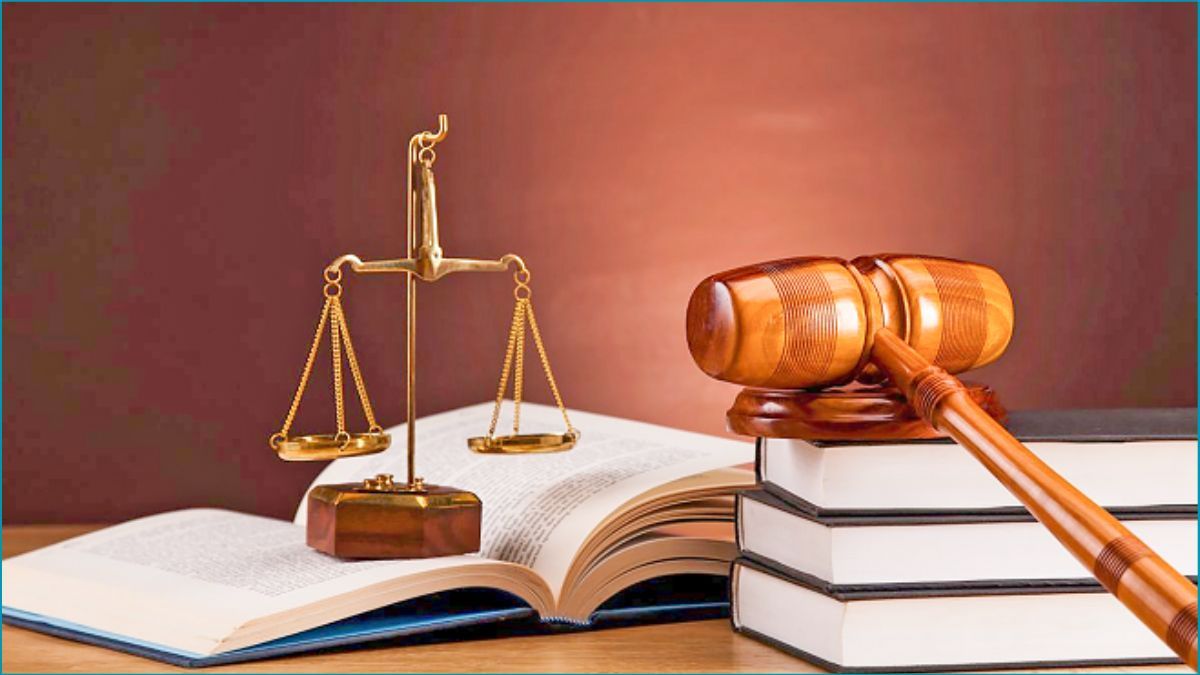
পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি আইন বাংলাদেশে। কিন্তু বাস্তবে প্রয়োগ নেই। এমনকি এসব আইন সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষ জানেই না। আইনের পাশাপাশি আছে নীতিমালা, রয়েছে আদালতের স্পষ্ট নির্দেশনাও; কিন্তু নেই কার্যকর প্রয়োগ।
এ ব্যর্থতাই আমাদের নাগরিক জীবনে এক নীরব বিশৃঙ্খলার জন্ম দিয়েছে। বাস্তবায়নের জন্য নিয়োজিত সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ও আছে। কিন্তু কার্যকর মনিটরিং ও প্রয়োগ না থাকায় সব উদ্যোগ মুখ থুবড়ে পড়েছে। এসব আইন যেন চাপা পড়ে আছে।
বাংলা ভাষা প্রচলন আইন : বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ২নং আইন), [ ৮ মার্চ, ১৯৮৭ ] বাংলাদেশের সংবিধানের ৩নং অনুচ্ছেদের বিধানকে পূর্ণরূপে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন। জাতীয় পার্টির শাসনামলে জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাসকৃত এই আইনের তৃতীয় ধারায় বলা হয়, ‘প্রবর্তন ও কার্যকরী ব্যবস্থা- (১) এই আইন প্রবর্তনের পর বাংলাদেশের সর্বত্র তথা সরকারি অফিস, আদালত, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যতীত অন্য সব ক্ষেত্রে নথি ও চিঠিপত্র, আইন আদালতের সওয়াল-জবাব এবং অন্যান্য আইনানুগ কার্যাবলী অবশ্যই বাংলায় লিখিতে হইবে। (২) ৩(১) উপ-ধারায় উল্লিখিত কোনো কর্ম যদি কোনো ব্যক্তি বাংলা ভাষা ব্যতীত অন্য কোনো ভাষায় আবেদন বা আপীল করেন তাহা হইলে উহা বেআইনি ও অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে। (৩) যদি কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী এই আইন অমান্য করেন তাহা হইলে উক্ত কার্যের জন্য তিনি সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপীল বিধির অধীনে অসদাচরণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাঁহার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপীল বিধি অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা করা হইবে।’ এমন একটি আইন পাস করার পর অনেকেই মনে করেছিলেন যে, বাংলা রাষ্ট্রভাষার এ দেশের আবশ্যকীয় ক্ষেত্রগুলোতে বাংলা প্রচলনের এক বিশাল অগ্রগতি হয়তো সাধিত হলো। যে অগ্রগতি ৪৮ সাধন করতে পারেনি, ৫২ সাধন করতে পারেনি, এমনকি স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানের রাষ্ট্রভাষার বিধান পর্যন্ত সাধন করে উঠতে পারেনি, এই আইন প্রবর্তনের ফলে তা-ই সম্ভব হয়ে উঠবে। কারণ এই আইন আদেশ করছে যে, সব সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং আদালতে বাংলা ব্যবহার করতে হবে; সব নথি ও পত্র, আদালতের সওয়াল-জবাব এবং অন্যান্য কাজকর্ম বাংলায় করতে হবে। আইনটিতে ব্যতিক্রমের যে বিধান রাখা হয়েছে, তা শুধু বৈদেশিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে। আইনটি সংশ্নিষ্ট সব ব্যক্তির জন্য বাধ্যতামূলক। এমন একটি আইন প্রবর্তিত হওয়ার পরও বাংলাসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলোতে স্বমহিমায় সম্পূর্ণত প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। বিশেষ করে আদালতে।
জনসমক্ষে ধূমপান : ধূমপান বন্ধে ২০০৫ সালে প্রণীত আইন অনুযায়ী, প্রকাশ্যে ধূমপানের জরিমানা ধরা হয়েছিল ৫০ টাকা। কিন্তু পরে ২০১৩ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনের সংশোধনী এনে জনসমাগমস্থলে ধূমপানের শাস্তির অর্থ ৫০ থেকে বাড়িয়ে ৩০০ টাকা করা হয়। কিন্তু আইন না জানা ও ভাঙায় অভ্যস্ত লোকজনের অবস্থা তাতে বদলায়নি। রাজধানীসহ দেশের অন্যান্য নগরে মানুষ প্রকাশ্যে পাবলিক প্লেসে ধূমপান করছে। তাদের কিছুই হচ্ছে না। উপরন্তু যারা প্রতিবাদ করছেন, তাদেরকেই বিভিন্ন ধরনের ঝামেলা সহ্য করতে হয়।
নদী দখল : জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যপরিধি বাড়ানোর জন্য ২০২০ সালে একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এ জন্য জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ‘জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন-২০২০’-এর খসড়া সরকারের কাছে পেশ করে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, এটি এত বছরেও আলোর মুখ দেখেনি। এই খসড়া আইনে নদী দখল ও দূষণের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি ১০ বছরের কারাদণ্ড বা ৫ কোটি টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান প্রস্তাব করা হয়েছিল। ২০১৩ সালের নদী রক্ষা কমিশন আইনে এ ধরনের অপরাধের জন্য কোনো শাস্তি নির্ধারিত ছিল না। পরিবেশ রক্ষার্থে নদ-নদী ভরাটের বিরুদ্ধে আদালতের আদেশও মানছে না ভূমিদস্যুরা। নদ-নদীও আজ হুমকির সম্মুখীন। ঢাকার পাশে যে ১৮টি নদী আছে, তার অবস্থা করুণ। এ নদীগুলো দূষিত হচ্ছে। কিন্তু নদী দূষণের বিষয়ে আইন থাকলেও কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। দুর্বল ব্যবস্থার জন্য নদীগুলো মরে যাচ্ছে। দেশে প্রায় ৯০০ নদী আছে। এসব নদীতে দখলদারের সংখ্যা ৫৭ হাজার।
খাদ্যে ভেজাল : খাদ্যে ভেজাল বা ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ মেশানোর অভিযোগে ১৪ বছরের জেল ও ১০ লাখ টাকার জরিমানার বিধান রেখে খাদ্যনিরাপত্তা আইন-২০১৩ এর নীতিগত অনুমোদন করেছিল বিগত সরকারের মন্ত্রিসভা। বিশেষ ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ডেরও বিধান রাখা হয়েছে। কিন্তু আইনটির কোনো প্রয়োগ নেই। বাজারে খাদ্যসামগ্রীতে ভেজাল দেওয়া বন্ধ হয়নি। মাছ, গোশত, ফল, শাকসবজি, দুধ, মিষ্টি ও ঘিতে ভোজাল দেওয়া হচ্ছে।
সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মাহাবুবুর রহমান বলেন, খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে কঠোর আইন আছে। ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক সাজার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তবুও ভেজাল রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই ভেজাল প্রতিরোধে আইনের পাশাপাশি প্রয়োজন জনসচেতনতা।
মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন : মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন আইন, ১৯৯৯ হলো যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান, সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং প্রতিস্থাপনের নিয়মকানুন নির্ধারণ করে। এই আইনটি জীবিত এবং মস্তিষ্ক-মৃত উভয় দাতাদের কাছ থেকে অঙ্গদানের অনুমতি দেয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বাণিজ্যিক ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। আইনটি ১৯৯৯ সালের ১৩ এপ্রিল কার্যকর হয় এবং পরবর্তীতে ২০১৮ সালে এতে কিছু সংশোধনী আনা হয়।
দেশে সবচেয়ে বেশি প্রতিস্থাপন হয় কিডনি। এরপরেই আছে চোখ ও লিভার। কিন্তু এসব প্রতিস্থাপনের হার খুবই কম। বিশেষ শর্তে নিকট আত্মীয় ছাড়াও দান করা যাবে দেহাঙ্গ। সোয়াপ ট্রান্সপ্ল্যান্ট বা ভিন্ন দুই গ্রহীতা ও তাদের আত্মীয়দের মধ্যে ব্লাড গ্রুপ মিলে গেলেই অঙ্গ দেওয়া-নেওয়া যাবে। অস্ত্রোপচার হতে হবে একই হাসপাতালে একই সময়ে। নিকট আত্মীয়ের মধ্যে ব্লাড গ্রুপ ম্যাচিং না হওয়া রোগী এবং তাদের আত্মীয়দের তথ্য নিয়ে করা হচ্ছে জাতীয় তথ্যভাণ্ডার। অঙ্গ বদলাবদলির পরিধিও বাড়ানো হচ্ছে। নিকট আত্মীয় হিসেবে ভাতিজা-ভাতিজি, ভাগ্নে-ভাগ্নি এবং সৎভাই-বোনকেও অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হচ্ছে। সেবার মান নিশ্চিতে অঙ্গ প্রতিস্থাপনে সরকারি হাসপাতালকেও অনুমোদন নিতে হবে।
ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) : রাজধানীর বিভিন্ন সড়কের মোড়, ফুটপাত, সড়ক বিভাজনের ওপর, বাজার, রেলস্টেশন ও বাসস্টেশনে ভবঘুরেদের উপস্থিতি ও আনাগোনা বেশি দেখা যায়। অনেক সময় মানসিক রোগীদের নগ্ন হয়ে ঘোরাফেরা মানুষের চরম বিরক্তির উদ্রেক করে। এছাড়া নাছোড়বান্দা ভিক্ষুকদের ভিক্ষাবৃত্তির কারণে বিরক্তির মধ্যে পড়ছেন পথচারীরা। রাজধানীর পরিত্যক্ত স্থান, খোলা জায়গা, গাছতলা ও খোলা মাঠ, পরিত্যক্ত ভবন, বস্তি, বিদ্যালয়, মসজিদ ও মাজারের বারান্দা, শপিং মার্কেটের সিঁড়িসহ যেখানে-সেখানে রাত্রিযাপন করে এসব ভিক্ষুক ও ভবঘুরে শ্রেণির মানুষ। এসব ভিক্ষুক ও ভবঘুরে শ্রেণির মানুষের জন্য বাংলাদেশে ‘ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন- ২০১১’ নামে আইন রয়েছে। এতে বলা আছে- সকল ভবঘুরে ও ভিক্ষুকদের আশ্রয়, পুনর্বাসন, চিকিৎসাসহ অন্যান্য দায়-দায়িত্ব বহন করবে সরকার। অথচ এই আইনটির প্রয়োগ না থাকায় ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তির পুনর্বাসনের অধিকার যেন ইটপাথরে চাপা পড়ে আছে।
আমাদের দেশে আইন আছে কিন্তু তার প্রয়োগ কতটুকু হচ্ছে? এ সম্পর্কে বাংলাদেশের খবরকে অ্যাড. আলাউল হোসেন মোল্লা বলেন, অনেক আইন আছে, কিন্তু প্রয়োগ হচ্ছে না। সচেতনতার অভাব আর যথাযথ প্রয়োগ না থাকায় সমাজে বাড়ছে আইন না মানার প্রবণতা।
ঢাকা জজ কোর্টের এপিপি কে এম খাইরুল আলম বলেন, আইন প্রয়োগের বিষয়ে আইন আছে। যে সমস্ত আইন প্রযোজ্য তা সেখানে প্রয়োগ করা হচ্ছে। একেবারে যে হচ্ছে না, তা নয়। এর মাধ্যমেই জনগণ উপকৃত হচ্ছেন। জনগণকে আগে আইন জানতে হবে। আইন না জানলে সেটা মানবে কী করে? এ জন্য সরকারকে সংশ্লিষ্ট আইন সম্পর্কে আরো বেশি প্রচার করতে হবে।
বিকেপি/এমবি