বাংলাদেশে মৃত্যুদণ্ডের প্রক্রিয়া আইন, বাস্তবতা
আইন ও আদালত ডেস্ক
প্রকাশ: ১৮ নভেম্বর ২০২৫, ১০:৫৭
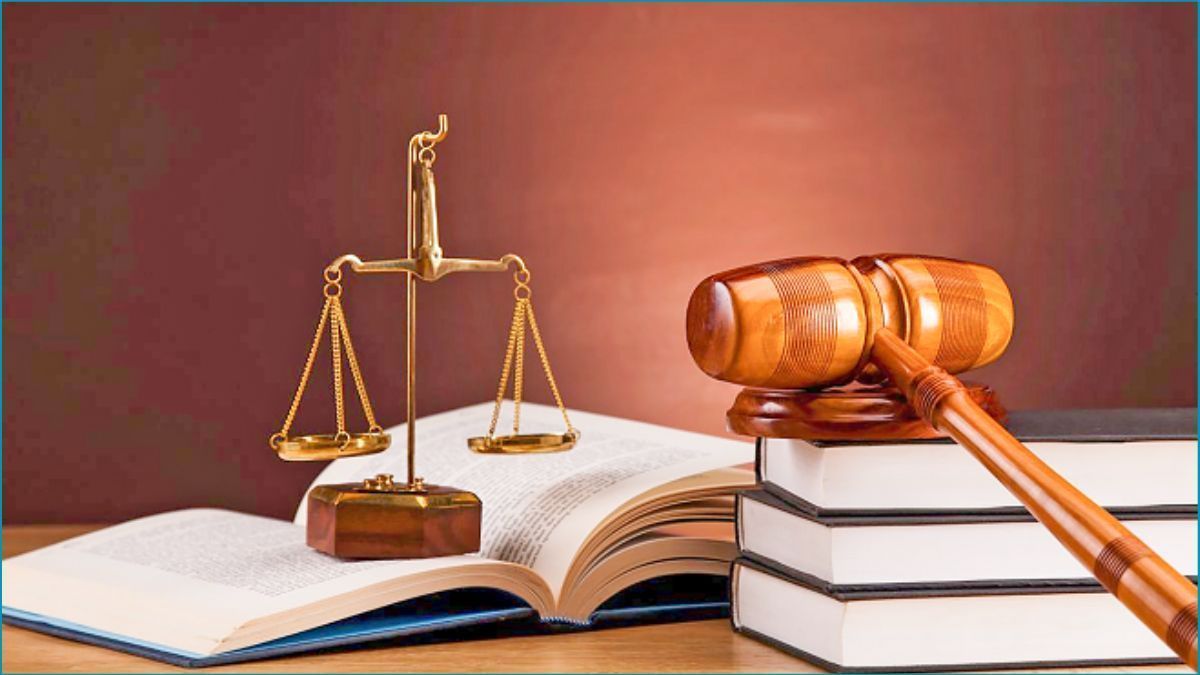
বাংলাদেশের ফৌজদারি আইনে মৃত্যুদণ্ড এখনও প্রচলিত একটি শাস্তি। আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি দেশের অন্যতম কড়া দণ্ডব্যবস্থা হলেও বাস্তব প্রয়োগ, বিচারিক পর্যালোচনা এবং নৈতিক প্রশ্নগুলো নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই রয়েছে নানা আলোচনা। এই প্রতিবেদনে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার ধাপ, আইনগত বাধ্যবাধকতা, কার্যকরকরণ এবং সংশ্লিষ্ট বিতর্ক তুলে ধরা হলো।
মৃত্যুদণ্ডের আইনগত ভিত্তি : বাংলাদেশের চবহধষ ঈড়ফব ১৮৬০- এর বিভিন্ন ধারায় হত্যাকাণ্ড, সন্ত্রাসী কার্যক্রম, ধর্ষণজনিত মৃত্যুসহ মোট কয়েকটি গুরুতর অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে। অন্যদিকে Code of Criminal Procedure (CrPC) ১৮৯৮- এর ৩৬৮ ধারায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে “গলায় ফাঁসি দিয়ে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত”। এ ছাড়া সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির কাছে দণ্ড মওকুফ বা লঘুকরণের ক্ষমতা রয়েছে। সরকারও বিশেষ পরিস্থিতিতে দণ্ড রিমিশন বা কমিউট করতে পারে।
কীভাবে মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয় : মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয় আইনের কয়েকটি ধাপ পেরিয়ে। যেমন বলা যায়, তদন্ত ও চার্জশিট। এক্ষেত্রে অপরাধ সংঘটনের পর পুলিশ বা সংশ্লিষ্ট সংস্থা তদন্ত সম্পন্ন করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করে। তারপর সাক্ষ্য-প্রমাণ বিশ্লেষণ শেষে বিচারক যদি অপরাধ প্রমাণিত মনে করেন এবং মামলাটি “মৃত্যুদণ্ডযোগ্য” ধরা হয়, তখন দণ্ড ঘোষণা করা হয়।
বাধ্যতামূলক হাইকোর্ট অনুমোদন (Death Reference) : বাংলাদেশে মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করলেই তা কার্যকর হয় না। প্রথমে রায়টি হাইকোর্ট বিভাগে বাধ্যতামূলক অনুমোদনের জন্য পাঠাতে হয়। হাইকোর্ট রায় বাতিল, বদল, হ্রাস বা অনুমোদন—যেকোনোটি করতে পারে। এরপর আপিল, রিভিউ ও মার্সি পিটিশন হতে পারে। হাইকোর্ট রায় বহাল রাখলে অভিযুক্ত সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে যাওয়ার সুযোগ পান। শেষ ধাপে থাকে রাষ্ট্রপতির কাছে দয়া প্রার্থনার আবেদন (mercy petition)।
কার্যকরকরণের ধাপ : সকল আইনি সুযোগ শেষ হওয়া- আপিল, রিভিউ ও মার্সি পিটিশনের সুযোগ শেষ হলে রায় কার্যকর করার অনুমতি দেয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। জেল কোড অনুসারে ফাঁসি কার্যকর- কারাগারে নির্ধারিত স্থানে সকালবেলায় দণ্ড কার্যকর করা হয়। উপস্থিত থাকেন ম্যাজিস্ট্রেট, কারা কর্তৃপক্ষ এবং চিকিৎসক। চিকিৎসক মৃত্যুর নিশ্চয়তা দিলে দণ্ডপ্রাপ্তের দেহ পরিবারের নিকট হস্তান্তর বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দাফন সম্পন্ন হয়।
প্রয়োগ বাস্তবতা : গবেষণা বলছে, বাংলাদেশে প্রতি বছর বহু মানুষ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেও কার্যকরকরণের সংখ্যা তুলনামূলক কম। প্রধানত দীর্ঘ বিচারপ্রক্রিয়া, আপিল ব্যবস্থা, রিভিউ এবং দয়া প্রার্থনার ধাপগুলো মিলিয়ে এই সময়কাল অনেক লম্বা হয়ে থাকে। এ ছাড়া বিশ্লেষকরা মনে করেন, দরিদ্র ও সামাজিকভাবে দুর্বল মানুষেরাই বেশি মৃত্যুদণ্ডের ঝুঁকিতে পড়ে, অপরাধ তদন্তে কারিগরি ঘাটতি, জবরদস্তি স্বীকারোক্তি ও প্রশ্নবিদ্ধ তদন্ত প্রক্রিয়া- মৃত্যুদণ্ডের ন্যায়বিচার নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি করে।
আইনি ও নৈতিক বিতর্ক : বাংলাদেশে মৃত্যুদণ্ড নিয়ে সবচেয়ে বড় বিতর্ক হলো- বিচারপ্রক্রিয়ার মান নিশ্চিত না হলে মৃত্যুদণ্ড অপূরণীয় ক্ষতি ডেকে আনতে পারে। আইনজীবী ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো বলছে- আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ড কেবল “সবচেয়ে গুরুতর অপরাধে” সীমাবদ্ধ থাকা উচিত, বিকল্প শাস্তির সুযোগ থাকলে বিচারকের স্বাধীন বিবেচনা নষ্ট হয় না, বিচারপ্রার্থী দরিদ্র মানুষের জন্য উন্নত আইনগত সহায়তা নিশ্চিত করা জরুরি।
অন্যদিকে মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে যারা, তারা মনে করেন গুরুতর অপরাধ দমনে এটি প্রয়োজনীয়, জনগণের ন্যায়বোধ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়, ভয়াবহ অপরাধে কঠোর শাস্তি সমাজে দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করে।
পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ: বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মতে বিচারপ্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ ও প্রযুক্তিনির্ভর করা। তদন্তে নির্যাতন বা জোরপূর্বক স্বীকারোক্তির অভিযোগের কড়া তদন্ত। সব মামলায় বিচারকের বিবেচনার সুযোগ রাখা—যাতে মামভেদে শাস্তি নির্ধারণ ন্যায়সংগত হয়। দরিদ্র আসামিদের জন্য দক্ষ আইনজীবীর নিশ্চয়তা। মৃত্যুদণ্ডের বিকল্প শাস্তির পথ নিয়ে জাতীয় আলোচনা। বাংলাদেশে মৃত্যুদণ্ডের আইনগত কাঠামো স্পষ্ট হলেও এর ন্যায়সঙ্গত প্রয়োগ এবং মানবাধিকার-মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য এখনো বিতর্কের বিষয়। অপরাধ দমন ও ন্যায়বিচারের ভারসাম্য রক্ষা করাই মৃত্যুদণ্ড-ব্যবস্থার মূল চ্যালেঞ্জ।
বিকেপি/এমবি




