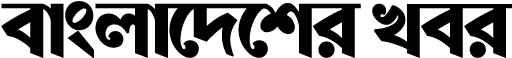বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ২১ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন
বাংলাদেশের প্রতিবেদক
প্রকাশ: ০৯ এপ্রিল ২০২৫, ১৪:৫৫

বাংলাদেশে বেসরকারি খাতের ঋণের প্রবৃদ্ধি ২১ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন অবস্থায় পৌঁছেছে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে কমে দাঁড়িয়েছে ৬ দশমিক ৮২ শতাংশে। টাকার অঙ্কে বেসরকারি খাতে ফেব্রুয়ারিতে বিনিয়োগ হয় ১৬ লাখ ৮৪ হাজার কোটি টাকা।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে, ফেব্রুয়ারি ২০০৪-এ বেসরকারি ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল ১৪ দশমিক ৪ শতাংশ। অর্থনীতিবিদরা জানান, এই প্রবৃদ্ধির নিম্নগামী প্রবণতা দেশের ব্যাংকিং খাতে গভীর সংকটের ইঙ্গিত দেয়। কারণ ক্রেডিট প্রবৃদ্ধি টানা সপ্তম মাসে হ্রাস পেয়েছে। তারা আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের পারস্পরিক শুল্ক আরোপের কারণে সংকট আরও বাড়তে পারে।
২০২৫ সালের জানুয়ারিতে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল ৭ দশমিক ১৫ শতাংশ, ডিসেম্বরে ৭ দশমিক ২৮ শতাংশ, নভেম্বরে ৭ দশমিক ৬৬ শতাংশ, অক্টোবরে ৮ দশমিক ৩ শতাংশ, সেপ্টেম্বরে ৯ দশমিক ২ শতাংশ, আগস্টে ৯ দশমিক ৮৬ শতাংশ, জুলাই মাসে ১০ দশমিক ১৩ শতাংশ এবং জুনে ৯ দশমিক ৮২ শতাংশ। ২০২২ সালের নভেম্বরে প্রবৃদ্ধির এই নিম্নগামী প্রবণতা শুরু হয়। তবে ২০২৪ সালের আগস্টে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংক জানুয়ারি মাসে ঘোষিত মুদ্রানীতিতে বেসরকারি খাতে ঋণ বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৯ দশমিক ৮ শতাংশ রাখলেও প্রকৃত প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য মাত্রার চেয়ে অনেক নিচে রয়েছে। অর্থনীতিবিদরা আশঙ্কা করছেন, এই ঋণ প্রবৃদ্ধির ধীরগতির কারণে শিল্প সম্প্রসারণ স্থগিত হয়ে যেতে পারে, নতুন বিনিয়োগের সুযোগ কমে যাবে এবং কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে।
বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ জাহিদ হুসেন বলেন, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা প্রধান ভূমিকা পালন করে বিভিন্ন কারণের সংমিশ্রণের ফলে বেসরকারি খাতের ঋণ কমে যাচ্ছে।
তিনি বলেন, রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল না হওয়া পর্যন্ত ঋণের চাহিদা পুনরুদ্ধার হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কারণ, পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনের আগে ব্যবসায়ীরা সতর্ক অবস্থানে রয়েছেন।
ঋণ বৃদ্ধির মন্দা ব্যবসায়িক খাতে দুর্বল চাহিদার ইঙ্গিত দেয় জানিয়ে জাহিদ বলেন, বেশিভাগ ব্যাংক ঋণ উৎপাদন এবং বিনিয়োগের জন্য প্রস্তুত ছিল।
তিনি আরও বলেন, বেশ কয়েকটি ব্যাংক বিশেষ করে যাদের বোর্ড সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক পুনর্গঠন করেছে, তারা বড় ঋণ প্রদানে সীমাবদ্ধ ছিল, যা ক্রেডিট সরবরাহকে আরও বাধাগ্রস্ত করেছিল।
ব্যাংকাররা বলছেন, শেখ হাসিনার পতনের পর একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বসানো সত্ত্বেও ব্যবসার পরিবেশ থমকে গেছে। তারা উচ্চ মূল্যস্ফীতি, ক্রমবর্ধমান ঋণের হার এবং দুর্বল ঋণ পুনরুদ্ধারকে প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করেছে।
বাংলাদেশ ব্যাংক গত ১০ ফেব্রুয়ারি-এর মুদ্রানীতির বিবৃতিতে স্বীকার করা হয়েছে যে, ঋণের মন্দা শুধুমাত্র নীতিগত হার বৃদ্ধির ফলে ছিল না। তবে ধীর আমানত বৃদ্ধি এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে অধিকহারে সরকারি ঋণ গ্রহণের ফলে এটি আরও জটিল হয়েছিল, যা বেসরকারি খাতকে আরও চাপে ফেলেছিল।
পলিসি রেট ১০ শতাংশে উন্নীত করাসহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংকোচন নীতি বাণিজ্যিক ঋণের হারকে ১৫ শতাংশের কাছাকাছি ঠেলে দিয়েছে। এই উচ্চ ধারের খরচ অনেক ব্যবসার জন্য ঋণকে অসহনীয় করে তুলেছে। বিগত সরকারের আমলে ব্যাপক ঋণ কেলেঙ্কারি ও অনিয়মের কারণে আমানতকারীদের মধ্যে আস্থা কমে গেছে।
মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান বলেন, দেশের চলমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে আর্থিক বাজারে ঋণের চাহিদা দুর্বল রয়েছে। তিনি বলেন, ব্যবসায়িক পরিবেশের উন্নতির সম্ভাবনা নেই।
মাহবুবুর আরও উল্লেখ করেন, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বাংলাদেশের আরও প্রভাবিত করতে পারে। তিনি লক্ষ্য করেন, বাংলাদেশি পণ্যের ওপর সাম্প্রতিক মার্কিন শুল্কারোপ ব্যবসায়িক ক্ষতি করতে পারে। যার ফলস্বরূপ ব্যাংকিং খাতে ঋণের চাহিদা আরও হ্রাস পাবে।
এ ছাড়া শেখ হাসিনার সরকারের সাথে যুক্ত থাকা বেশকিছু ব্যবসায়ী আইনি চাপের বরাত দিয়ে এবং ব্যবসা করার জন্য প্রতিকূল পরিবেশের অভিযোগ এনে কার্যক্রম কমিয়ে দিয়েছেন; যা দেশে ঋণের চাহিদা এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রভাব ফেলেছে। ক্রমবর্ধমান খেলাপি ঋণ, উল্লেখযোগ্য আমানত উত্তোলন এবং তারল্য ঘাটতির কারণেও ব্যাংকিং খাতের ক্রেডিট বাড়ানোর ক্ষমতা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়েছে।
দেশের ব্যাংকিং খাতে অ-পারফর্মিং ঋণের পরিমাণ ২০২৪ সালে বেড়েছে, যা ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের ১ দশমিক ৪৫ লাখ কোটি টাকার তুলনায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি।
কিছু ব্যাংক দৈনিক নগদ চাহিদা মেটাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং বড় ব্যাংকগুলোর কাছে সহায়তা চেয়েছে। উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি, বৈদেশিক মুদ্রার অস্থিরতা এবং চলমান ডলারের ঘাটতির মতো অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ সংকটকে আরও জটিল করে তুলেছে। বিনিময় হার দুই বছরে ৯০ টাকা থেকে বেড়ে প্রতি মার্কিন ডলার ১২২ টাকায় উন্নীত হয়েছে, যা আমদানি ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়েছে।
এএইচএস/এটিআর