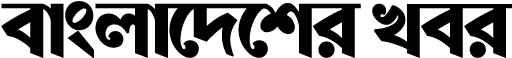-6864d57e8acaf.jpg)
পিআর পদ্ধতি বা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation, PR) নির্বাচন পদ্ধতি বিশ্বের অনেক গণতান্ত্রিক দেশে জনপ্রিয় একটি নির্বাচন ব্যবস্থা। এই পদ্ধতিতে ভোটের অনুপাতে রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীদের আসন বণ্টন করা হয়, যাতে জনগণের ভোটের প্রতিফলন সঠিকভাবে সংসদ বা নির্বাচিত সংস্থায় প্রতিফলিত হয়। বাংলাদেশে এই পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা সম্প্রতি জোরদার হয়েছে, বিশেষ করে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের পর। এই আলোচনায় আমরা পিআর পদ্ধতির সংজ্ঞা, এর প্রকারভেদ, সুবিধা-অসুবিধা এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে আলোচনা করব।
পিআর পদ্ধতি নির্বাচন কী?
পিআর পদ্ধতি এমন একটি নির্বাচন ব্যবস্থা, যেখানে কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী গোষ্ঠী যত শতাংশ ভোট পায়, তত শতাংশ আসন তাদের দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো দল ৩০% ভোট পায়, তবে তারা মোট আসনের প্রায় ৩০% পাবে। এটি ‘ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট’ (FPTP) বা ‘উইনার টেকস অল’ পদ্ধতির বিপরীত, যেখানে একজন প্রার্থী সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও পুরো আসনটি জিতে নেন। পিআর পদ্ধতি নিশ্চিত করে যে, সংখ্যালঘু দল বা ছোট দলগুলোও তাদের সমর্থনের অনুপাতে প্রতিনিধিত্ব পায়।
পিআর পদ্ধতির প্রধান লক্ষ্য হলো ভোটের প্রতিটি অংশকে কার্যকর করা, যাতে কোনো ভোট ‘নষ্ট’ না হয়। বিশ্বের ৮০টির বেশি দেশ, যেমন জার্মানি, নিউজিল্যান্ড, সুইডেন, এবং দক্ষিণ আফ্রিকা, এই পদ্ধতি ব্যবহার করে। বাংলাদেশে এই পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হলেও, এটি এখনো প্রয়োগ করা হয়নি।
পিআর পদ্ধতির প্রকারভেদ
পিআর পদ্ধতির বিভিন্ন রূপ রয়েছে, যার মধ্যে তিনটি প্রধান :
পার্টি লিস্ট পিআর (Party-List PR) : এই পদ্ধতিতে ভোটাররা কোনো দলের পক্ষে ভোট দেন, এবং দলগুলো আগে থেকে প্রার্থী তালিকা তৈরি করে। আসন বণ্টন ভোটের শতাংশের ভিত্তিতে হয়। এটি দুই ধরনের হতে পারে:
ক্লোজড লিস্ট : ভোটাররা শুধু দলের জন্য ভোট দেন, প্রার্থী নির্বাচনের কোনো সুযোগ থাকে না। দলের তালিকার শীর্ষে থাকা প্রার্থীরা আসন পান।
ওপেন লিস্ট : ভোটাররা দলের পাশাপাশি নির্দিষ্ট প্রার্থীদের জন্য ভোট দিতে পারেন, যা প্রার্থী নির্বাচনে ভোটারদের প্রভাব দেয়।
সিঙ্গল ট্রান্সফারেবল ভোট (STV) : এই পদ্ধতিতে ভোটাররা প্রার্থীদের পছন্দের ক্রম অনুযায়ী র্যাংক করেন। একটি নির্দিষ্ট কোটা (যেমন, ড্রুপ কোটা) পূরণের মাধ্যমে প্রার্থীরা নির্বাচিত হন। অতিরিক্ত ভোট বা নির্মূল প্রার্থীদের ভোট পরবর্তী পছন্দের প্রার্থীদের কাছে স্থানান্তরিত হয়। এই পদ্ধতি আয়ারল্যান্ড ও মাল্টায় জনপ্রিয়।
মিক্সড-মেম্বার প্রোপোরশনাল (MMP) : এই পদ্ধতিতে ভোটাররা দুটি ভোট দেন—একটি স্থানীয় প্রার্থীর জন্য এবং অন্যটি দলের জন্য। স্থানীয় আসনগুলো FPTP পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়, এবং অতিরিক্ত আসনগুলো দলীয় ভোটের অনুপাতে বণ্টন করা হয়। জার্মানি ও নিউজিল্যান্ড এই পদ্ধতি ব্যবহার করে।
পিআর পদ্ধতির সুবিধা
পিআর পদ্ধতি গণতন্ত্রকে আরও সমৃদ্ধ ও প্রতিনিধিত্বমূলক করে। এর কিছু উল্লেখযোগ্য সুবিধা হলো :
সুষ্ঠু প্রতিনিধিত্ব : পিআর পদ্ধতি নিশ্চিত করে যে ছোট দল এবং সংখ্যালঘু গোষ্ঠী তাদের সমর্থনের অনুপাতে প্রতিনিধিত্ব পায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো দল ১০% ভোট পায়, তারা ১০% আসন পাবে, যা FPTP-তে প্রায়শই সম্ভব হয় না।
ভোটের নষ্ট কমে : FPTP পদ্ধতিতে যারা জয়ী প্রার্থীকে ভোট দেননি, তাদের ভোট বৃথা যায়। পিআর পদ্ধতিতে প্রায় প্রতিটি ভোটই ফলাফলের অংশ হয়, যা ভোটারদের মধ্যে নির্বাচনের প্রতি আস্থা বাড়ায়।
বৈচিত্র্যময় প্রতিনিধিত্ব : পিআর পদ্ধতি জাতিগত, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে। এটি বাংলাদেশের মতো বৈচিত্র্যময় সমাজে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
জার্মান্ডারিং হ্রাস : FPTP পদ্ধতিতে নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ (জার্মান্ডারিং) সম্ভব। পিআর পদ্ধতিতে বহু-সদস্যের নির্বাচনী এলাকা থাকায় এই সমস্যা অনেকাংশে কমে।
নতুন দলের উত্থান : পিআর পদ্ধতি ছোট ও নতুন দলগুলোকে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেয়, যা রাজনৈতিক প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করে।
পিআর পদ্ধতির অসুবিধা
প্রতিটি ব্যবস্থার মতো পিআর পদ্ধতিরও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে :
জটিলতা : পিআর পদ্ধতি, বিশেষ করে STV, ভোট গণনা ও বণ্টনের ক্ষেত্রে জটিল। এটি ভোটারদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে।
দুর্বল স্থানীয় সংযোগ : ক্লোজড লিস্ট পিআর-এ ভোটাররা শুধু দলের জন্য ভোট দেন, ফলে নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং নির্বাচনী এলাকার মধ্যে সংযোগ দুর্বল হতে পারে।
গঠনমূলক সরকারের অভাব : পিআর পদ্ধতিতে একক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া কঠিন, ফলে জোট সরকার গঠনের প্রয়োজন হয়। এটি কখনো কখনো রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণ হতে পারে।
ছোট দলের প্রভাব : অতিরিক্ত ছোট দলের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পিআর পদ্ধতি
বাংলাদেশে বর্তমানে FPTP পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, যেখানে একক প্রার্থী সর্বোচ্চ ভোট পেলে আসন জিতেন। এই পদ্ধতিতে বড় দলগুলো বেশি সুবিধা পায়, এবং ছোট দল বা স্বতন্ত্র প্রার্থীরা প্রায়শই প্রতিনিধিত্ব থেকে বঞ্চিত হয়। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশে নির্বাচনী সংস্কারের দাবি জোরালো হয়েছে। অনেকে মনে করেন, পিআর পদ্ধতি বাংলাদেশের রাজনৈতিক বৈচিত্র্যকে আরও ভালোভাবে প্রতিফলিত করতে পারে।
বাংলাদেশে পিআর পদ্ধতির সম্ভাব্য সুবিধা
ছোট দলের প্রতিনিধিত্ব : বাংলাদেশে ছোট দলগুলো, যেমন গণফোরাম বা বিকল্পধারা, প্রায়ই FPTP-তে আসন পায় না। পিআর পদ্ধতি তাদের জন্য সুযোগ তৈরি করবে।
জনগণের আস্থা বৃদ্ধি : ভোটের প্রতিটি অংশ গুরুত্ব পাওয়ায় ভোটারদের মধ্যে নির্বাচনের প্রতি আস্থা বাড়বে।
সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব : ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষিত আসন ছাড়াও পিআর পদ্ধতি তাদের স্বাভাবিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে পারে।
সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ
জটিল বাস্তবায়ন : বাংলাদেশের মতো দেশে, যেখানে শিক্ষার হার এবং নির্বাচনী সচেতনতা এখনও উন্নয়নশীল নয়, সেখানে পিআর পদ্ধতি বোঝানো ও বাস্তবায়ন করা কঠিন হতে পারে।
রাজনৈতিক অস্থিরতা : জোট সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে, কারণ বড় দলগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্র।
দলীয় আধিপত্য : ক্লোজড লিস্ট পিআর-এ দলীয় নেতৃত্ব প্রার্থী নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, যা গণতান্ত্রিক স্বচ্ছতা হ্রাস করতে পারে।
বাংলাদেশে পিআর পদ্ধতির সম্ভাবনা
২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশে নির্বাচনী সংস্কারের দাবি উঠেছে। অন্তর্বর্তী সরকার, ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে, নির্বাচনী সংস্কার কমিশন গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পিআর পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা জোরদার হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, এটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট সমাধানে সহায়ক হবে, আবার কেউ মনে করেন, এটি জনগণ ও প্রতিনিধিদের মধ্যে দায়বদ্ধতা হ্রাস করতে পারে।
বাংলাদেশে পিআর পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য কিছু প্রস্তাব
মিক্সড-মেম্বার পিআর : এটি স্থানীয় প্রতিনিধিত্ব এবং আনুপাতিক বণ্টনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে।
জনসচেতনতা বৃদ্ধি : পিআর পদ্ধতির জটিলতা বোঝাতে ভোটার শিক্ষা কার্যক্রম প্রয়োজন।
পরীক্ষামূলক প্রয়োগ : স্থানীয় নির্বাচনে পিআর পদ্ধতি পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করে এর কার্যকারিতা যাচাই করা যেতে পারে।
পিআর পদ্ধতি নির্বাচন গণতন্ত্রকে আরও প্রতিনিধিত্বমূলক ও ন্যায়সঙ্গত করতে পারে। বাংলাদেশের মতো দেশে, যেখানে রাজনৈতিক বিভক্তি ও বড় দলের আধিপত্য দীর্ঘদিনের সমস্যা, পিআর পদ্ধতি একটি নতুন সম্ভাবনা। তবে, এর বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক ইচ্ছা, স্বচ্ছ নীতি এবং জনসচেতনতা অত্যন্ত জরুরি। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশ একটি নতুন রাজনৈতিক যুগে প্রবেশ করেছে। পিআর পদ্ধতি এই নতুন যুগে গণতন্ত্রের ভিত্তিকে আরও মজবুত করতে পারে, যদি এটি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়।
লেখক : মুহাম্মদ নূরে আলম, সাংবাদিক ও কলামিস্ট