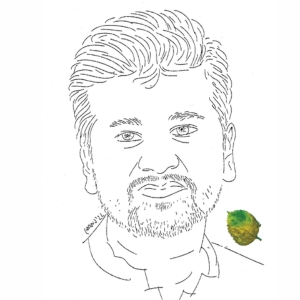যাত্রাবাড়ীর ঘটনায় বিবিসির ‘অনুসন্ধান’ নিয়ে কিছু ভাবনা
প্রকাশ: ১০ জুলাই ২০২৫, ১৫:৫৮

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে সংঘটিত ভয়াবহ প্রাণহানি নিয়ে বিবিসি আই ও বিবিসি বাংলা সম্প্রতি যে অনুসন্ধান প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, তা প্রকাশের পরপরই বাংলাদেশে এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। কেউ এটিকে রাষ্ট্রীয় দমনপীড়নের প্রমাণ বলে দেখাচ্ছেন, অন্যদিকে কেউ একে খণ্ডিত, একপাক্ষিক এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলছেন। এ ধরনের ‘অনুসন্ধানী’ প্রতিবেদনের বেলায় সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো— প্রতিবেদনটি সাংবাদিকতাগত মান, তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা ও নৈতিকতার দিক থেকে কতটা সংহত?
বিবিসির প্রতিবেদনটি মূলত দুটি অংশে বিভক্ত— প্রথম অংশে যাত্রাবাড়ীতে পুলিশের গুলিতে ৫২ জন নিহত হওয়ার দাবি; দ্বিতীয় অংশে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি ফোনালাপ। প্রতিবেদনে বলা হয়, তারা ভিডিও, সিসিটিভি ফুটেজ, ড্রোন চিত্র এবং কিছু প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তদন্ত চালিয়েছে।
প্রথম অংশে কিছু নতুন ভিডিও উপস্থাপন করে গুলির সূত্রপাত, বিক্ষোভকারীদের পালানোর চিত্র এবং পুলিশের আচরণ বিশ্লেষণ করা হয়। দ্বিতীয় অংশে যে অডিও উপস্থাপন করা হয়েছে, সেটিকে শেখ হাসিনার কণ্ঠ বলে দাবি করে একটি ফরেনসিক পরীক্ষার কথা জানানো হয়েছে।
এই প্রতিবেদন প্রকাশের পরপরই আওয়ামী লীগপন্থী একাধিক সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাক্টিভিস্ট দাবি করেছেন, শেখ হাসিনার এই অডিওটি ২০১৬ সালের ‘হোলি আর্টিজান হামলা’র সময়কার। এমনকি তাদের কেউ বিবিসিকে ‘চ্যালেঞ্জ’ ছুঁড়ে দিয়ে বলেছেন— এই অডিওর পূর্ণ রেকর্ড প্রকাশ করতে হবে এবং তা ‘ঠিক কবে, কোন পরিস্থিতিতে, কার সঙ্গে আলাপ চলছিল— এই সব তথ্য পরিষ্কার করতে হবে।’
সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন ‘চ্যালেঞ্জ’ বিবিসির নজর এড়িয়ে যাওয়ার কথা না। তবে চব্বিশ ঘণ্টার বেশি সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও বিবিসি এ বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা বা বক্তব্য দেয়নি। অথচ সাংবাদিকতার মান নিশ্চিতে বিষয়টি স্পষ্ট করার দায় তাদেরই। একদিন পরে বিবিসি ‘শেখ হাসিনার গুলির নির্দেশের ফাঁস হওয়া অডিও রেকর্ডিং যেভাবে যাচাই করেছে বিবিসি’ শিরোনামে আরেকটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সেখানে জাতিসংঘের তদন্তকারী দলের তথ্যমতে জুলাই-আগস্টের আন্দোলন ও সহিংসতায় কত জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, বিশেষ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটররা কী বলছেন ইত্যাদি জাতীয় বক্তব্য দিয়ে ফাঁস হওয়া রেকর্ডিংকে ১৮ জুলাইয়ের দাবি করে কণ্ঠস্বরটি যে শেখ হাসিনার তা কী উপায়ে নিশ্চিত হয়েছে বিবিসি, তাই তুলে ধরেছে। কিন্তু এটি ১৮ জুলাই ২০২৪-এরই কল রেকর্ড— এমন দাবির পক্ষে বলেছে, ‘ফাঁস হওয়া অডিওটি সম্পর্কে জানেন এমন একটি সূত্র বিবিসিকে জানিয়েছে’। যখন কোনো পক্ষ থেকে কল রেকর্ডটির সময়কাল নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে তখন এতটুুক বক্তব্যই প্রমাণের জন্য যথেষ্ট না বলে মনে করি।
বিবিসির ফরেনসিক যাচাই কেবলমাত্র এটুকু নিশ্চিত করে বলেছে— ‘এটি শেখ হাসিনার কণ্ঠ’। কিন্তু এটি কবেকার, কী প্রসঙ্গে বা কোন প্রেক্ষাপটে বলা হয়েছিল, কার সাথে ছিল এই কথোপকথন এবং এর পূর্ণাঙ্গতা কেমন ছিল— এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর উত্তর বিবিসি’র প্রতিবেদনে অনুপস্থিত।
এ ধরনের রাজনৈতিকভাবে ‘চরম স্পর্শকাতর’ অডিও যদি পুরোনো সময়ের কোনো প্রেক্ষাপটের হয়, আওয়ামী লীগ অ্যাক্টিভিস্টরা যেমনটা দাবি করছেন এবং তাকে নতুন বা ভিন্ন প্রেক্ষাপটের বলে প্রতিষ্ঠা করা হয়— তবে তা সাধারণ পাঠকের কাছে ভয়াবহ বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে। ভুল ব্যাখ্যা, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রতিক্রিয়া এবং রাজনৈতিক উত্তেজনার উৎস হয়ে উঠতে পারে। সেজন্য এই ধরনের তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে সাংবাদিকের নৈতিক দায়িত্ব বহুগুণ বেড়ে যায়।
বিবিসির মতো একটি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম যখন একটি সংবেদনশীল সময়ের সরকারপ্রধানের কথোপকথন ‘প্রমাণ’ হিসেবে উপস্থাপন করে, তখন শুধু ভয়েস ভেরিফিকেশনই যথেষ্ট নয়। তার সঙ্গে পূর্ণ অডিও প্রকাশ, সময়কাল নিশ্চিতকরণ এবং কথোপকথনের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ থাকা উচিত ছিল। এই তিনটির অনুপস্থিতি বিভ্রান্তির উদাহরণ তৈরি করে থাকে।
যদি এই অডিও সত্যিই ২০২৪ সালের ১৮ জুলাইয়ের হয়, তাহলেও প্রতিবেদনে স্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল— সেদিন দেশের পরিস্থিতি কী ছিল? আন্দোলনের প্রকৃতি কেমন ছিল? সরকারপ্রধানের এই নির্দেশনায় যদি কোনো দমননীতি প্রতিফলিত হয়ে থাকে, তা বুঝতে হলে সেদিনকার সার্বিক অবস্থা জানাও জরুরি। বিবিসি এই প্রেক্ষাপটও উপস্থাপন করেনি।
অন্যদিকে, যদি দাবি করা অডিও পুরোনো হয়, তবে এর ব্যবহার আরও গুরুতর সমস্যা তৈরি করে— কারণ অন্য সময়ের, অন্য প্রেক্ষাপটে বলা কোনো বক্তব্যকে বর্তমান সময়ের সহিংসতার নির্দেশ বলে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা একধরনের তথ্যবিকৃতি।
বিবিসির এই অনুসন্ধান প্রতিবেদনটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণে কিছু প্রমাণ হাজির করলেও, এতে তথ্য নির্বাচন, বক্তব্য উপস্থাপন এবং প্রেক্ষাপট উপেক্ষার যে দুর্বলতা রয়েছে তা একে অসম্পূর্ণ করে তোলে। এর চেয়েও বড় কথা, অডিও ক্লিপ সংক্রান্ত অংশটির সামগ্রীক চিত্র ও ব্যাখ্যার অনুপস্থিতি সাংবাদিকতার শুদ্ধতা ও সততার মানদণ্ডেও প্রশ্নের জন্ম দেয়।
একটি বড় সত্য যদি যথাযথভাবে না বলা হয়, বা ভুল প্রেক্ষাপটে বলা হয়— তবে সেটিও অর্ধসত্য হয়ে ওঠে। একটি গণমাধ্যম হিসেবে বিবিসির উচিত ছিল এসব প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের পূর্ণ উত্তর দেওয়া এবং অডিওর উৎস ও সম্পূর্ণতা স্পষ্ট করা। তাহলে আলোচিত-সমালোচিত এই প্রতিবেদনটিকে যারা বিভ্রান্তিকর বলছেন, তাদের তা বলার অবকাশ থাকত না।
মেহেদী হাসান শোয়েব : লেখক, প্রকাশক, বিতার্কিক; শিফট ইনচার্জ, বাংলাদেশের খবর
- বাংলাদেশের খবরের মতামত বিভাগে লেখা পাঠান এই মেইলে- bkeditorial247@gmail.com