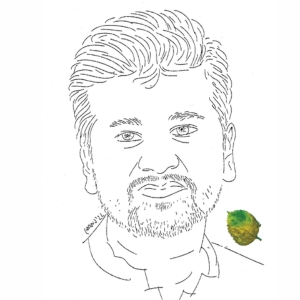-6877683b167a9.jpg)
একটা সময় ছিল, যখন মধ্যবিত্ত শ্রেণি মানেই ছিল—প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষিত, নিয়মিত বেতনভোগী, একটি শারীরিক কর্মস্থলে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে উপার্জনকারী মানুষ, যার পরিচয় সমাজে ওই কর্মস্থল বা প্রতিষ্ঠানের কাজ দিয়ে তৈরি হতো। সে শিক্ষক হতে পারতেন, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা সরকারি কর্মকর্তা। তার অবস্থান ছিল দৃশ্যমান, সংজ্ঞায়িত, নিরাপদ। অথচ আজকের বাংলাদেশে আমরা মধ্যবিত্তের ভেতরেও একটা ‘নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি’র উত্থান দেখছি। তারা অনেকাংশেই ‘কর্মসংস্থানহীন’, অথবা ‘কাজে না থেকেও ব্যস্ত’, চাকরিহীন হয়েও ‘কর্পোরেট’ মোহে আক্রান্ত। আবার নিজেকে ‘উদ্যোক্তা’ বলে দাবি করলেও অনেকের আয়ের নিশ্চয়তা নেই। এই পরিবর্তিত শ্রেণিটি এক অদ্ভুত আত্মপরিচয়ের সংকটে ভুগছে, যা কেবল অর্থনৈতিক নয়, মনস্তাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক এবং রাষ্ট্র-নির্ভর সামাজিক রূপান্তরের প্রতিচ্ছবি।
আজকের বাংলাদেশে তাই মধ্যবিত্তের সংজ্ঞা আর প্রথাগত শিক্ষিত বেতনভোগী নয়। যুবসমাজ এখন ‘উদ্যোক্তা’, ‘ফ্রিল্যান্সার’ বা ‘ক্রিয়েটর’ বলে নিজেকে পরিচিত করছে। কিন্তু বাস্তবে এসব উপায়ে অধিকাংশের আয়-সংস্থাপনই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এই অনিশ্চয়তার জাঁতাকলে পড়ে তারা ‘মাঝামাঝি’ একটি পরিচয়ে জীবন কাটাচ্ছে—যা তাদেরকে না চাকরি, না স্থিতিশীলতা, আর না কাঙ্ক্ষিত মর্যাদা প্রদান করছে। ফলে বাস্তবে অনেককেই আয়ের অনিশ্চয়তার ভেতরেই কেবল ‘মধ্যবিত্ত’ ট্যাগ ধরে রাখার চাপ বয়ে বেড়াতে হচ্ছে।
পরিচয় সংকটের জন্ম
একজন বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া তরুণ, যিনি মাস্টার্স শেষে দুই বছর ধরে ‘ফ্রিল্যান্সিং’ করছেন—ঘরে বসে বিদেশি ক্লায়েন্টদের জন্য ডিজাইন করছেন, অথচ কখনো অফিস যাননি, সহকর্মীও নেই। সমাজ তাকে ‘বেকার’ বলেও স্বীকার করে না, আবার স্থায়ী উপার্জন না থাকায় ‘কর্মজীবী’ বলার ভাষাও খুঁজে পায় না। এরকম হাজার হাজার তরুণ-তরুণী ছড়িয়ে আছে শহরে-গ্রামে, যারা হয়ত নিজের পকেটখরচ চালায়, হয়ত মাসে কিছু আয় করে—তবে কখনো চাকরির নিশ্চয়তা পায় না, সামাজিক সম্মান বা স্থিতি পায় না। তারা এক অদ্ভুত ‘in-between’ অবস্থা তৈরি করে চলেছে, যেখানে মধ্যবিত্তের পরিচয় আর আগের মতো নির্ভরযোগ্য নয়।
প্রযুক্তি ও ফাঁপা প্রতিশ্রুতির মধ্যবিত্ত
গত এক দশকে ই-কমার্স, ফেসবুকভিত্তিক অনলাইন উদ্যোক্তা সংস্কৃতি, ডিজিটাল মার্কেটিং, ইনফ্লুয়েন্সার পেশা ইত্যাদির প্রসার এই শ্রেণির আত্মপ্রবঞ্চনা আরও বাড়িয়েছে। চাকরি নেই, তবে অনলাইন স্টোর আছে। অফিস নেই, কিন্তু প্রোফাইলে 'Founder at...' লেখা। বহুক্ষেত্রে এগুলোর পেছনে নেই কোনো আয়ব্যয় পরিকল্পনা, নেই সুশৃঙ্খল প্রতিষ্ঠানগত কাঠামো। নিজের ঘরই অফিস, নিজের ভাই বা বোন কর্মী এবং আয়ের উৎসও অস্থায়ী। অথচ সামাজিকভাবে তারা মধ্যবিত্ত জীবনযাপন করতে বাধ্য—শিক্ষা, পোশাক, প্রযুক্তি ব্যবহার, বিনোদনের ধরন—সবই মধ্যবিত্ত শ্রেণির, কিন্তু অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা অধিকাংশেরই হচ্ছে না এসব নানা নামের ডিজিটাল মাধ্যমে।
সফলতা এখন যেন পণ্যের মতোই বিক্রি হচ্ছে—একটা স্কিল শেখো, অনলাইন কোর্সে নাম লেখাও, নিজেকে ‘ব্র্যান্ড’ বানাও, তাহলেই লাখ টাকা আয় সম্ভব! ফেসবুক–ইউটিউব খুললেই চোখে পড়ে এমন শত শত বিজ্ঞাপন, যেখানে বলা হয়—তুমি চাইলেই পারবে, সাফল্য শুধু ইচ্ছের ব্যাপার, ইত্যাদি ইত্যাদি চটকদার কথাবার্তা। আর এসবের পেছনে থাকেন একদল ‘মোটিভেশন স্পিকার’, যারা স্টিভ জবস, এলন মাস্ক বা জুকারবার্গের মতো দুনিয়ার সেরা সফল ব্যক্তিদের গল্প বলে বোঝাতে চান—তুমি চাইলেই এমন হতে পারো। কিন্তু বাস্তবতা এতটা সহজ নয়, আর এই ‘চাইলেই পারবে’ দর্শন অনেক সময় তরুণদের জীবনের সবচেয়ে বড় ‘প্রতারণার ফাঁদ’ হয়ে দাঁড়ায়।
কারণ—যে যেভাবেই ভাবুক না কেনো, বাস্তবতা এটাই যে সবার পক্ষে সেরা হওয়া সম্ভব নয়। এক কোটি মানুষের মধ্যে একজন হয়ত জুকারবার্গ হতে পারে। বাকিরা তেমন হওয়ার চেষ্টা করলেও এক পর্যায়ে ব্যর্থ হয়ে হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এই ‘চাইলেই পারবে’ দর্শনে বড় সমস্যা হলো, এটি ব্যর্থতার জায়গাটিকে অস্বীকার করে। তরুণদের শেখানো হয় না যে, ব্যর্থতা স্বাভাবিক, প্রত্যেকেই নিজের জায়গা থেকে সীমিত সাফল্য নিয়ে বাঁচতে পারে। বরং বোঝানো হয়—তুমি সেরা না হলে তুমি ব্যর্থ। আর এখানেই শুরু হয় আত্মপ্রবঞ্চনা, হতাশা আর একধরনের মানসিক চাপ।
বেশিরভাগ মোটিভেশন বক্তা মধ্যবিত্ত তরুণদের দুর্বল মুহূর্তে ধরেন—যখন চাকরি নেই, কখনো স্বপ্ন আবার কখনো হতাশায় ভোগে। তখন তারা বলেন, ‘এই স্কিল শিখে আয় শুরু করো, সফল হও’।—কিন্তু বলেন না, সফল না হলে কী হবে? এসব উপায়ে চেষ্টায় কতজন পারছে আসলে সফল হতে? সেই অনুপাতটা কেমন? কতজন মাঝপথে হতাশ হয়ে থেমে যাচ্ছে? এগুলো নেই তাদের গল্পে। নেই বাস্তব পরিসংখ্যান, নেই ঝুঁকির দিক। ফলে তরুণরা উৎসাহে ঝাঁপ দেয়, কিছুদিন পরে বোঝে—এই পথ এতটা মসৃণ নয়। আর তখন অনেকে আর ফিরে দাঁড়াতে পারে না। হতাশা, আত্মবিশ্বাসের ভাঙন, নিজের ওপর সন্দেহ—এইসব নিয়ে অসংখ্য মধ্যবিত্ত তরুণ বস্তুত হারিয়ে যায়। অনেকে আত্মহত্যার মতো পথও বেছে নিতে বাধ্য হয়।
মোটিভেশন প্রয়োজন, নিঃসন্দেহে। কিন্তু সেই মোটিভেশন যদি বাস্তবতাবিবর্জিত হয়, যদি তা অতিশয়োক্তিতে ভরা হয়, তাহলে তা সাহায্যের চেয়ে ক্ষতিই বেশি করে। বাস্তবতা হলো—সবার জীবনের পথ আলাদা। কেউ উদ্যোক্তা হবে, কেউ চাকরি করবে, কেউ হয়ত শিল্পী, কেউ কৃষক। সবার সফলতার সংজ্ঞাও এক নয়। এই বহুত্বের জায়গা থেকেই তরুণদের সাহস দেওয়া উচিত। না হলে এই ‘তুমি চাইলেই পারবে’—দর্শন এক সময় হয়ে দাঁড়ায় ‘তুমি পারোনি, কারণ তুমি অযোগ্য’। তাই তুমি ‘ব্যর্থ’—এরকম মানসিক বিষে পরিণত হয় বিষয়গুলো।
কর্মসংস্থান না থাকলে মধ্যবিত্ত কীভাবে টেকে?
একটি সমাজ তখনই মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি করতে পারে, যখন সেখানে আয়ভিত্তিক গতিশীলতা থাকে—নিচ থেকে ওপরে ওঠার সিঁড়ি তৈরি হয়। অথচ বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী কর্মসংস্থান কমে এসেছে। বিসিএস কিংবা ব্যাংক নিয়োগের বাইরে ভালো চাকরির সুযোগ হাতেগোনা। অধিকাংশ কর্পোরেট চাকরিও প্রজেক্টভিত্তিক, অস্থায়ী। যারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে বের হচ্ছে, তারা হয় বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে, নয়তো ব্যস্ত সামাজিক মাধ্যমে একটি 'কৃত্রিম ব্যস্ততা' তুলে ধরতে। বাস্তবে কোনো কর্মসংস্থান না থাকা মানে, সামাজিক মর্যাদাও ধীরে ধীরে ক্ষয় হচ্ছে।
মধ্যবিত্ত মানে এখন মানসিক রোগী?
একটি আন্তর্জাতিক গবেষণায় দেখা গেছে, অনিশ্চিত পেশাজীবী শ্রেণির মধ্যে বিষণ্নতা, আত্মঘৃণা, একাকিত্ব এবং নিঃসঙ্গতা অনেক বেশি। বাংলাদেশে এর নিঃশব্দ প্রতিফলন প্রতিদিনই আমরা দেখছি। দিনে চা-কফির দোকানে বড় স্বপ্ন নিয়ে কথা বলা তরুণরা রাতে নিজের ঘরে গিয়ে গভীর শূন্যতায় ভোগে। চাকরি নেই, ভবিষ্যৎ নেই, কিন্তু পরিবার-সমাজের কাছে নিজেকে ‘সফল’ প্রমাণ করার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে যেতে হয় প্রতিনিয়ত। ফলে বাংলাদেশে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি বড় অংশ বর্তমানে একটি অদৃশ্য কিন্তু গভীর মানসিক স্বাস্থ্য সংকটে আটকে পড়েছে। এই শ্রেণির মানুষেরা শিক্ষিত, শহরমুখী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং সামাজিক মর্যাদার প্রতি সংবেদনশীল। কিন্তু বাস্তব জীবনে তারা চরম অনিশ্চয়তা, বেকারত্ব এবং আত্মপরিচয়ের ঘোর সংকটে নিমজ্জিত।
এই আভ্যন্তরীণ টানাপড়েন, পারিবারিক চাপ, সামাজিক তুলনা এবং নিজেকে প্রমাণ করার বেদনাদায়ক আকাঙ্ক্ষা থেকেই জন্ম নেয় এক ধরনের নীরব মানসিক রোগ—যা শুরু হয় উদ্বেগ দিয়ে, পরে তা গড়িয়ে পড়ে বিষণ্নতা, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, আত্মগ্লানির মতো ভয়ানক পর্যায়ে।
২০১৯ সালে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য জরিপ (NIMH) অনুসারে, বাংলাদেশে ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে প্রতি পাঁচজনে একজন মানসিক সমস্যায় ভোগেন। কিন্তু এই সমস্যায় ভোগা মানুষের সিংহভাগই চিকিৎসার সুযোগ পান না, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে এই ‘সাহায্য চাওয়া’ আরও কম দেখা যায়। কারণ, তাদের পরিচয়টাই গড়ে উঠেছে আত্মসম্মান আর সামাজিক অবস্থানের উপর, তাই মানসিক দুর্বলতা প্রকাশ করাকে তারা অপমানজনক ভাবেন।
এই শ্রেণির তরুণেরা যখন একের পর এক চাকরির পরীক্ষা দিয়ে ব্যর্থ হয়, তখন আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরে। যখন বন্ধুরা বিদেশে চলে যায় বা কেউ অনলাইনে আয় শুরু করে, তখন নিজের জীবনের স্থবিরতাকে তারা ব্যর্থতা মনে করে। ফলাফল হয়—একটি মনস্তাত্ত্বিক সংকট, যা মধ্যবিত্তকে একা করে দেয় নিজের ভেতরেই। কেউ কাউন্সেলিং নিতে চায় না, মানসিক চিকিৎসা তো দূরের কথা—তারা ‘নরমাল’ থাকার অভিনয় করে দিনের পর দিন, এবং এই অভিনয়ের ভেতরেই তাদের ভিতরটা ক্ষয়ে যেতে থাকে।
বাংলাদেশের উদীয়মান মধ্যবিত্ত তরুণদের একাংশ এখন চাকরি নেই, আয় নেই, কিন্তু প্রত্যাশার বোঝা নিয়ে ছুটে চলেছে। তারা দিনে হয়ত ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামে উদ্যমী ক্যাপশন দেয়, কিন্তু রাতে ঘুম আসে না। তারা হয়ত বন্ধুদের সঙ্গে ক্যাফেতে আড্ডা দেয়, কিন্তু নিজের মূল্য এবং যোগ্যতা নিয়ে সন্দিহান।
এই বাস্তবতায় বলা যেতে পারে—মধ্যবিত্ত মানে এখন অনুচ্চারিত মানসিক রোগী, যার রোগটা সে নিজে বুঝতে পারলেও স্বীকারও করতে পারে না।
আত্মপ্রতারণা বনাম আত্মরক্ষা
বাধ্য হয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষেরা নিজেদের খুব ‘প্রোডাকটিভ’, ‘উন্নয়নমুখী’, ‘ইনোভেটিভ’ এবং ‘সফল’ হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করতে সামাজিক মাধ্যমে ঢাকঢোল পেটাচ্ছে। কিন্তু আদতে এসব হয়ে যাচ্ছে একরকম আত্মপ্রতারণা। দিনশেষে এটি মানসিক আত্মরক্ষার উপায় মাত্র। না হলে তারা ভেঙে পড়বে। একজন তরুণ যখন বলে, ‘আমি উদ্যোক্তা’, বা ‘আমি কনটেন্ট ক্রিয়েটর’—তার পেছনে প্রমাণ হিসেবে কোনো ট্যাক্স রেকর্ড নেই, কোনো মাসিক ইনকাম নেই—তবু সে বলছে, আসলে বলতে বাধ্য হচ্ছে হয়ত। কারণ, চুপ করে বসে থাকা, বা কিছু করতে না পারা মানে পরাজিত হওয়া।
মধ্যবিত্তের এই নতুন শ্রেণির তরুণদের জীবনে এক ভয়াবহ মিশ্র অনুভব ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে—তারা জানে বাস্তবতা কঠিন, কিন্তু নিজেকেই তারা প্রতিদিন ভুল বোঝাতে থাকে। নিজের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে গিয়ে তারা এক ‘আত্মপ্রতারণার জালে’ আটকে যায়।
যেমন—কেউ হয়ত তিন বছর ধরে ফ্রিল্যান্সিং শিখছে, কিন্তু এখনো কোনো প্রকল্প পাচ্ছে না। তবুও সে নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে লিখে রাখে : Freelance Web Developer | Digital Marketer | Visionary Entrepreneur. ইত্যাদি। কিংবা কোনো তরুণ ইউটিউবে ভিডিও দেয়, নিজে কোনো ইনকাম করতে পারেনি সেখান থেকে—তবুও বলে, ‘এই পেশায় প্রচুর সম্ভাবনা!’ এই কথাগুলো আসলে অনেক সময় নিজের ভেতরে তৈরি হওয়া শূন্যতাকে ঢাকতে বলা আত্মপ্রতারণার বাক্য।
তবে এই প্রতারণা খুব সরল নয়—এটাকে অনেক সময় ‘আত্মরক্ষা’ হিসেবে ব্যবহার করতে চেষ্টা করেন তরুণেরা। তারা জানেন যে, তারা একরকম অভিনয় করছেন—নিজের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে। কিন্তু এই অভিনয়ই হয়ত তাদের ক্ষণিকের মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখছে। এটি একদিকে আত্মরক্ষা হলেও কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে এটি সামগ্রিক আত্মপ্রবঞ্চনায় পরিণত হয়।
এই চক্রবূহ্যে প্রবেশ করার পর, তরুণরা প্রতিটি দিন কাটায় এক দোলাচলে—আমি কি সত্যিই কিছু করছি, নাকি শুধু করার ভান করছি? এই প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে কেউ হতাশায় ঢুকে পড়ে, কেউ নতুন কোর্সে ভর্তি হয়, কেউ আত্মবিশ্বাস দেখাতে ফেসবুকে ‘সাকসেস স্টোরি’ বানায়। এইভাবে তারা বাস্তবতাকে মুছে ফেলে—এক ধরনের কল্পিত আত্মপরিচয়ের আড়ালে।
তাদের অনেকেই হয়ত জানেই না—এই আত্মপ্রতারণা মানসিক অবসাদকে আরও গভীর করে তোলে ধীরে ধীরে।
প্রশ্ন হলো—এই মধ্যবিত্ত তরুণদের কী দোষ? তারা কি উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রতারণা করছে? তা কিন্তু না মোটেও। বরং তারা বাঁচার চেষ্টা করছে। কিন্তু সমাজ যখন তাদের কেবল সাফল্যের গল্প শোনায়, ব্যর্থতার সত্যিটা না বলে। আর মধ্যবিত্ত সমাজের বড় এক সংকট হলো, ব্যর্থকে গ্রহণ করতে রাজি না হওয়া।
মধ্যবিত্তের বিপন্নতা রাষ্ট্রের বিপন্নতা
এই তথাকথিত ‘নতুন মধ্যবিত্ত’র অবস্থা শুধু অর্থনৈতিক সংকট নয়, এটি সমাজের ভবিষ্যৎ স্থিতি নিয়ে বড় ধরনের প্রশ্ন তোলে। কোনো রাষ্ট্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হলো তার মধ্যবিত্ত শ্রেণি। কারণ এই শ্রেণিই সাধারণত দেশের শিক্ষিত, উৎপাদনশীল, নীতিনিষ্ঠ এবং মূল্যবোধসম্পন্ন জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। তারা রাষ্ট্রের সুশাসনের পক্ষে থাকে, গণতন্ত্রকে ধারণ করে, অর্থনীতিকে সচল রাখে এবং সংস্কৃতি ও চিন্তার ক্ষেত্রেও নেতৃত্ব দেয়। ফলে মধ্যবিত্ত যদি বিপন্ন হয়, তাহলে তা কেবল একটি শ্রেণির সংকট নয়, বরং তা রাষ্ট্রের ভিত দুর্বল হয়ে পড়ার লক্ষণ।
বাংলাদেশের বাস্তবতায় দেখা যাচ্ছে, নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির বড় একটি অংশ এখন কর্মসংস্থানহীন, পরিচয়হীন এবং আত্মবিশ্বাসহীন হয়ে পড়েছে। তারা না পাচ্ছে স্থায়ী চাকরি, না পাচ্ছে নির্ভরযোগ্য আয়, না পাচ্ছে সামাজিক মর্যাদা। এই অবস্থায় দীর্ঘদিন থাকার ফলে তাদের মধ্যে জন্ম নিচ্ছে এক ধরনের চাপা ক্ষোভ ও হতাশা, যা একসময় ব্যক্তিগত গ্লানির সীমা পেরিয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিই সন্দেহ ও অবিশ্বাসের জন্ম দেয়।
একজন মধ্যবিত্ত তরুণ যখন তার শিক্ষার যথাযথ ব্যবহার করতে পারে না, তখন সে হয় নিজের ভেতর গুটিয়ে যায়, নয়তো রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থাকে দোষ দিয়ে বিরাগভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এই মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার প্রবণতাই এক সময় রূপ নেয় গভীর নাগরিক বিচ্ছিন্নতায়। তখন রাষ্ট্র আর নিজের বলে মনে হয় না, বরং এক ধরনের শত্রু মনে হতে থাকে। এই জায়গাটি অত্যন্ত বিপজ্জনক, কারণ তখন নাগরিকরা শুধু অসন্তুষ্ট নয়, তারা আর বিশ্বাসও করে না।
এই বিশ্বাসহীনতা ধীরে ধীরে সমাজে একটি অবক্ষয়ের সংস্কৃতি তৈরি করে, যেখানে তরুণেরা ন্যায়নীতি বা সততার পথে থাকার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তারা সহজেই মেরুকৃত রাজনীতি, চরমপন্থা বা বিভ্রান্তিমূলক পথের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এর ফলে রাষ্ট্র তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ—মানবিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক শক্তিকে হারায়।
এ কারণেই বলা যায়, মধ্যবিত্তের বিপন্নতা মানে কেবল ব্যক্তিগত স্বপ্নভঙ্গতা নয়, বরং তা একটি রাষ্ট্রের ভবিষ্যতের বিপন্নতা। রাষ্ট্রের অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি—সবকিছুই ক্ষতিগ্রস্ত হয় যখন তার সবচেয়ে দায়িত্ববান শ্রেণিটি নিজেকে অনিরাপদ, অপ্রয়োজনীয় ও অসহায় মনে করতে থাকে।
শেষ কথা
বাংলাদেশের নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি এক অদৃশ্য অথচ প্রবল সঙ্কটে রয়েছে—তা কেবল কর্মসংস্থানের নয়, বরং আত্মপরিচয়ের। তারা সমাজে একধরনের প্রতিশ্রুতিশীল শ্রেণি হিসেবে বিবেচিত হলেও বাস্তবে তারা নিজেরাই জানে না, তারা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। তাদের শিক্ষা আছে, কিন্তু কাজ নেই; স্বপ্ন আছে, কিন্তু পথ নেই; সম্মান চায়, কিন্তু বাস্তবতা বারবার অপমান করে। এই শ্রেণির ভেতরকার অস্থিরতা এখন নিছক ব্যক্তিগত বেদনা নয়, তা হয়ে উঠছে সামষ্টিক উদ্বেগ।
যেখানে একটি সমাজের সবচেয়ে সচেতন, সম্ভাবনাময় শ্রেণি—যুব মধ্যবিত্ত—নিজেকে মূল্যহীন, অসফল বা নিরর্থক ভাবতে শুরু করে, সেখানে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎও ধীরে ধীরে ঘোলাটে হয়ে পড়ে। হতাশ, বিভ্রান্ত ও আত্মপ্রতারণায় নিমজ্জিত এই শ্রেণির মানুষরা হয়তো আজ ক্ষোভ পোষণ করছে চুপচাপ, কিন্তু আগামীকাল সেই ক্ষোভ রূপ নিতে পারে সামাজিক অস্থিরতা, আত্মঘাতী নিস্তেজতা কিংবা সহিংস প্রতিবাদে।
এই সংকটের সমাধান কোথায়? সমাধান শুধু কর্মসংস্থানের অঙ্কে নেই, শুধু ডেটা দিয়ে ব্যাখ্যা করেও এই সংকট মেটানো যাবে না। দরকার একটি সহানুভূতিশীল রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি, দরকার পরিবার-সমাজ-শিক্ষা-নীতিনির্ধারকদের সম্মিলিত বোঝাপড়া—যেখানে একজন মানুষ শুধু আয়ক্ষমতা দিয়েই মূল্যায়িত হবে না, বরং তার আত্মপরিচয়, মানসিক ভারসাম্য এবং ধৈর্যকে মর্যাদা দেওয়া হবে।
এই প্রজন্মকে বাঁচাতে হলে তাদের আত্মপরিচয় রক্ষার লড়াইকে রাষ্ট্রীয় অগ্রাধিকার দিতে হবে। না হলে, নতুন মধ্যবিত্ত শুধু কর্মসংস্থানহীনই থাকবে না—তারা হয়ে উঠবে আত্মহীন, উদ্দেশ্যহীন, মূল্যহীন এক ক্লান্ত শ্রেণি। আর সে শ্রেণির ক্লান্তি আসলে গোটা জাতির ক্লান্তির পূর্বাভাস।