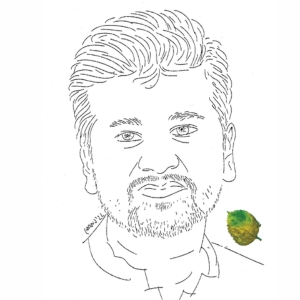ডাকসুর ফলাফলে বোঝা যাবে দেশের রাজনীতির গতিপ্রকৃতি, সমীকরণ কি এত সরল?
প্রকাশ: ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:০৯
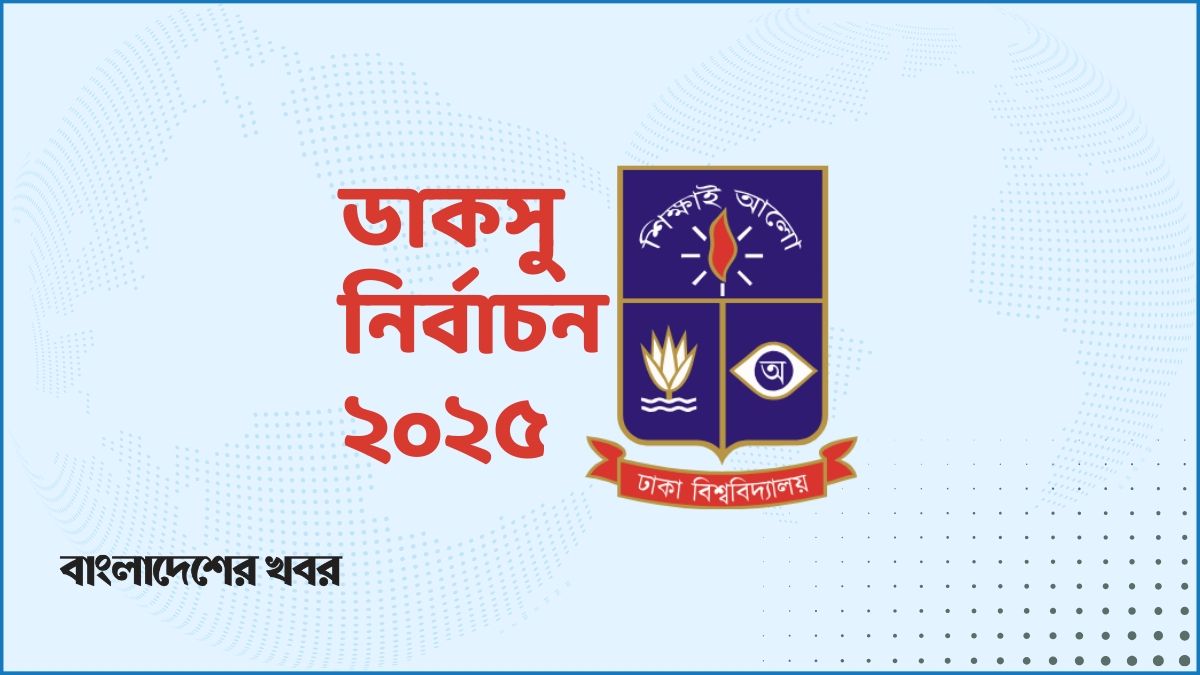
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ— ডাকসু শুধু একটি ছাত্র সংগঠন নয়; এটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ, সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান— জাতির প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে এই বিশ্ববিদ্যালয় ও এর ছাত্রসমাজ নেতৃত্ব দিয়েছে। একসময়কার বাস্তবতায় ঢাবির ক্যাম্পাসের অবস্থা এমন ছিল যে দেশের রাজনৈতিক রূপরেখা প্রায়শই এখানে অলিখিতভাবে নির্ধারিত হতো।
আজকের দিনে এসে সেই ধারণা আবারও আলোচনায় এসেছে ডাকসু নির্বাচনের সূত্র ধরে। দেশের বিশ্লেষক ও বুদ্ধিজীবীদের বড় একটি অংশ মনে করছেন, আসন্ন ডাকসুর নির্বাচনী ফলাফলে তরুণ প্রজন্মের রাজনৈতিক মানসিকতার প্রতিফলন দৃশ্যমান হবে। তাদের মতে, এখানেই বোঝা যাবে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধে তরুণদের বিশ্বাস, গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতি তাদের আস্থা। সেইসাথে এই বিশ্লেষক ও বুদ্ধিজীবীরা বলছেন, দেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতির গতিপথও নাকি স্পষ্ট হয়ে উঠবে ডাকসুর ফলাফলের ভেতর দিয়েই। প্রশ্ন হচ্ছে— এই ধারণা কতটা বাস্তবসম্মত? এখন কি বাস্তবতা অনেক বেশি জটিল না? এই সময়ে এসে ডাকসুর ফলাফলের ভিত্তিতে জাতীয় রাজনীতির গতিপ্রকৃতি অনুধাবনের চেষ্টা বিভ্রান্তিকর না কি?
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অবজ্ঞা করার সুযোগ নেই। এটি স্বাধীনতার সোপান নির্মাণের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলাকে অবজ্ঞা করে রাষ্ট্রভাষা উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে প্রথম প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর আসে এখানকার ছাত্র সমাজের কাছ থেকে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান—সব ক্ষেত্রে ছাত্ররা নেতৃত্ব দিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাবি প্রতিরোধের প্রতীকী ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছিল, আর ২৫ মার্চের কালরাতে পাকিস্তানি সেনারা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে হত্যাযজ্ঞ চালায়। স্বাধীনতার পরেও আশির দশকে এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন, নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান—সব ক্ষেত্রে ডাকসু নেতারা জাতীয় রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অবজ্ঞা করার সুযোগ নেই। এটি ছিল স্বাধীনতার সোপান নির্মাণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলাকে অবজ্ঞা করে রাষ্ট্রভাষা উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে প্রথম প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শোনা যায় এখানকার ছাত্রসমাজের কাছ থেকে। সেই আন্দোলন ১৯৫২ সালের ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে নতুন মাত্রা পায়। এরপর ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনে ছাত্ররা সামরিক সরকারের চাপিয়ে দেওয়া শিক্ষানীতি প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে ছাত্ররা নেতৃত্ব দেয় জাতিকে; তাদের আন্দোলনের চাপেই আইয়ুব খানের পতন ঘটে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাবি রূপ নেয় প্রতিরোধের প্রতীকী ঘাঁটিতে— যে কারণে পাকিস্তানি সেনারা ২৫ মার্চের কালরাতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে হত্যাযজ্ঞ চালায়। স্বাধীনতার পরেও ঢাবির ছাত্ররা জাতীয় রাজনীতির চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে। আশির দশকে এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন ছিল অদম্য। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র সমাজের সম্মিলিত শক্তি স্বৈরাচার পতন ঘটায়। ডাকসুর নেতাদের অনেকেই পরবর্তীতে জাতীয় রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বে আসীন হন। এই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত থেকেই হয়ত আজও রাজনীতি বিশ্লেষকরা ডাকসু নির্বাচনের ফলাফলের ভেতরে জাতীয় রাজনীতির ভবিষ্যত দেখতে পাচ্ছেন বা দেখতে চাচ্ছেন।
এই ধারাবাহিকতার বাস্তবতা সম্ভবত এখন আর নেই। বরং তা ভেঙে গেছে অনেক আগেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর দেশের মেধার একমাত্র, এমনকি প্রধান কেন্দ্রবিন্দুও নয় সেভাবে আর। একসময়কার ‘দেশের সেরা মেধাবীদের একমাত্র ঠিকানা’ হয়ে ওঠার গৌরব অনেক দিন ধরেই হারিয়েছে এ বিশ্ববিদ্যালয়। আজ দেশের অসংখ্য মেধাবী শিক্ষার্থী ইচ্ছাকৃতভাবে ভর্তি পরীক্ষাই দেয় না আর এখানে। তারচেয়ে স্বাচ্ছন্দবোধ করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে, অন্তত একটু স্থিতিশীল ভালো পরিবেশে পড়াশোনাটা করতে পারার নিশ্চয়তার জন্য। কিংবা বিদেশে, যেখানে তারা গবেষণা, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের বৃহত্তর সুযোগ পাচ্ছে। ঢাবির একাডেমিক মানের অবক্ষয়, গবেষণার সীমাবদ্ধতা, প্রশাসনিক অদক্ষতা এবং সবচেয়ে বড় সংকট— হল সংস্কৃতি। যে আবাসিক হল একসময় ছিল সাংস্কৃতিক চর্চা ও মুক্ত চিন্তার আঙিনা, তা আজ বহু ক্ষেত্রে দখলদারিত্ব, সহিংসতা ও দলীয় কোন্দলের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। ছাত্রজীবনের মৌলিক স্বাধীনতা, নতুন প্রজন্মের সৃজনশীল বিকাশ— এসবই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এই অনৈতিক অস্থির সংস্কৃতির কারণে। ফলে ডাকসুর নির্বাচনে যারা অংশ নিচ্ছেন তারাই দেশের তরুণ সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছেন— এ কথা আর সেভাবে বলা যায় না। আজকের তরুণ প্রজন্মের বৃহত্তর অংশ ছড়িয়ে আছে দেশের ৫০টিরও বেশি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে, কয়েকশ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে, মেডিকেল কলেজ ও টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে। তাদের রাজনৈতিক চেতনা ও আকাঙ্ক্ষা বহুমাত্রিক, যা কেবল ঢাবি ক্যাম্পাসের নির্বাচনের ফলাফলে কোনোভাবেই প্রতিফলিত হতে পারে না বলে মনে করি।
পাশাপাশি বর্তমানে জাতীয় রাজনীতি একটি জটিল অবস্থায় আছে। আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নির্বাহী আদেশে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জাতীয় পার্টি নিষিদ্ধ করার দাবি উঠেছে। এদি ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, সংবিধান অনুযায়ী পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের সুযোগ নেই বলে প্রচলিত পদ্ধতিতেই নির্বাচন হবে। বিএনপি প্রচলিত পদ্ধতিতে ভোটের পক্ষে থাকলেও জামায়াতসহ এনসিপি ও আরও কিছু রাজনৈতিক দল পিআরের দাবিতে অবস্থান নিয়েছে। এমনকি পিআর ছাড়া নির্বাচনে তারা যাবে না বলেও ঘোষণা দিয়েছে কোনো কোনো দল। সরকারের পক্ষ থেকে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন দফায় দফায় বৈঠক করে নানা প্রেসক্রিপশন দিচ্ছে। তবে বছর পেরিয়ে গেলেও ঐক্যমত ও সংস্কারের কোনো নমুনা দৃশ্যমান হচ্ছে না। ফলে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছে। এমনকি নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতে সত্যি সত্যি হবে কিনা সে বিষয়েও রাজনীতি বিশ্লেষকরা নিশ্চিত নন।
এই প্রেক্ষাপটে ডাকসুর যে বা যারাই বিজয়ী হোক, তাদের আদর্শ বা পন্থী রাজনৈতিক দল জাতীয় রাজনীতিতে সমভাবে প্রভাব ফেলতে পারবে— এমনভাবে ভাবার সুযোগ নেই বলেই মনে করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোটে অংশগ্রহণ করা তরুণদের রাজনৈতিক সক্রিয়তার একটি সীমিত প্রতিফলন মাত্র। জাতীয় নির্বাচনে তরুণদের অংশগ্রহণের আগ্রহ বা ভোট দেওয়ার প্রবণতাও ডাকসু নির্বাচন থেকে প্রমাণিত হয় না। তদুপরি, যদি শেষপর্যন্ত আগামী নির্বাচন আওয়ামী লীগ ছাড়া হয়, যেমনটা প্রস্তুতি চলছে, তাহলে এই দলের ফিক্সড যে ‘ভোট ব্যাংক’ ভোটের বাক্সে তাদের কী ভূমিকা হবে, জাতীয় রাজনীতির সমীকরণকে তারা কতটা প্রভাবিত করবে— এ প্রশ্নও গুরুত্বপূর্ণ।
অতএব, ডাকসু নির্বাচনের ফলাফলের মাধ্যমে জাতীয় রাজনীতির ভবিষ্যত বোঝার চেষ্টা বিভ্রান্তিকর বলেই মনে করি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন আর দেশের মেধার একমাত্র বা প্রধানতম কেন্দ্রবিন্দু নয়। আজকের তরুণ সমাজ বহুমাত্রিক। কেউ বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতিতে সক্রিয়, কেউ সামাজিক আন্দোলনে, কেউ উদ্যোক্তা, কেউ আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে। তাদের রাজনৈতিক চেতনা ডাকসুর ভোটের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হওয়ার সুযোগই নেই।
ডাকসু নির্বাচন নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। এটি একটি গণতান্ত্রিক অনুশীলন, যা শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়। তবে এর সীমাবদ্ধতা বোঝা জরুরি। ডাকসুর ফলাফল একটি প্রতীক, যা ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারের ধারাবাহিকতা বহন করে, কিন্তু জাতীয় রাজনীতির জটিলতা ও গতিপ্রকৃতির পূর্ণ প্রতিচ্ছবি নয়। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় রাজনীতি এখন এমন এক বিন্দুতে দাঁড়িয়ে, যেখানে দলীয় সংঘাত, নির্বাচন পদ্ধতির বৈচিত্র্য, ভোট ব্যাংকের বাস্তবতা এবং তরুণ প্রজন্মের বহুমাত্রিক সক্রিয়তা একসাথে জটিল সমীকরণ তৈরি করছে।
মেহেদী হাসান শোয়েব : লেখক, প্রকাশক, বিতার্কিক; শিফট ইনচার্জ, বাংলাদেশের খবর
- বাংলাদেশের খবরের মতামত বিভাগে লেখা পাঠান এই মেইলে- bkeditorial247@gmail.com