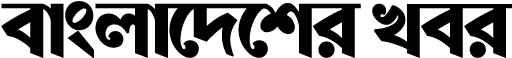তিস্তার ভাগ্য বদলের চেষ্টায় জনতার মশাল মিছিল
খন্দকার সিহাবুর রহমান
প্রকাশ: ১৭ অক্টোবর ২০২৫, ২০:০৫
-68f24eabcc55a.png)
তিস্তার বাঁধের কাজ দ্রুত শুরু করার দাবিতে পাঁচ জেলার মানুষ হাতে মশাল নিয়ে মিছিল করেছে। বিএনপি নেতা জনাব দুলুর নেতৃত্বে এই মশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হয় ১৬ অক্টোবর। যদিও প্রচারের ঘাটতির কারণে তিস্তার ন্যায্য পানির হিস্যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জোরালোভাবে তুলে ধরা সম্ভব হয়নি, মিছিলের মূল লক্ষ্য ছিল নভেম্বরের মধ্যে বাঁধের কাজ শুরু করার জন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে চাপ সৃষ্টি করা।
ভারত তিস্তা নদী থেকে প্রতিবছর প্রায় ৮৫ শতাংশ পানি সরিয়ে নেয়, যার ফলে উত্তরাঞ্চলে সৃষ্টি হয়েছে এক প্রকার মরুভূমি। গজলডোবা বাঁধের পাশে একটি ফিডার ক্যানেল দিয়ে ভারতের দিকে পানি সরিয়ে নেওয়া হয়-যেমনটি আমরা ফারাক্কা বাঁধের ক্ষেত্রেও দেখি (যেখানে ভারতে নদীটির নাম গঙ্গা, আর বাংলাদেশে পদ্মা)। গুগল ম্যাপে তাকালেই দেখা যায়, বাংলাদেশের দিকে তিস্তা শুকিয়ে যাচ্ছে, আর নদীর তীরবর্তী মানুষজন আজও এক মরীচিকার মতো অপেক্ষা করছে পানির জন্য।
তিস্তার বাঁধের প্রয়োজনীয়তা কেবল কোনো দলের দাবির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়-এটি উত্তরবঙ্গের সার্বজনীন সমস্যা। তাই যে কোনো দলের ডাকে সবাই একসঙ্গে হওয়া উচিত।
১৯৭৬ সালের ১৬ মে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রথম ফারাক্কা লং মার্চের সূচনা করেন। হাজার হাজার মানুষ সেই মিছিলে অংশ নেন, যা পৌঁছেছিল চাঁপাইনবাবগঞ্জের কানসাট পর্যন্ত। তখনই প্রথমবার বাংলাদেশের গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা দাবি করে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে দু’দফা চিঠি পাঠানো হয়। এরপর থেকেই যেন আমরা নদীর গুরুত্ব ভুলে গেছি-অথবা ভুলিয়ে রাখা হয়েছে।
ভারত গঙ্গা চুক্তির পর থেকে আর কোনো নদী নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তি করতে চায়নি। কারণ, একবার যদি গঙ্গার মানদণ্ডে চুক্তি হয়, তবে অন্য আন্তর্জাতিক নদীগুলিতেও বাংলাদেশ ন্যায্য হিস্যা দাবি করবে-যা ভারত কখনোই চায় না।
ড. কে. এল. রাও ১৯৭৫ সালের ১৫ ডিসেম্বর প্রকাশ করেন তার “এ ন্যাশনাল ওয়াটার পলিসি ফর ইন্ডিয়া”। এর লক্ষ্য ছিল ভারতের সব রাজ্যে পানির প্রবাহ নিশ্চিত করা এবং একটি জাতীয় জলব্যবস্থা তৈরি করা। এই নীতির আওতায় তিস্তার পানি পশ্চিমবঙ্গে সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু হয়। পরবর্তীতে গঙ্গা, পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের পানিও ক্যানেল করে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব করা হয়-যার বিরোধিতা করে বাংলাদেশ।
রংপুর বিভাগে শিল্পকারখানা গড়ে না ওঠার অন্যতম কারণ হলো নদীপথের অভাব। নদীগুলোর গভীরতা কমে গেছে, অনেক নদী প্রায় শুকনো। ফলে পরিবহন খরচ বেড়েছে, সময় ও সুযোগ কমে গেছে। তাই এখানকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত।
এমন প্রেক্ষাপটে তিস্তা নিয়ে আন্দোলন ও মশাল মিছিল ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। ভারত বুঝে ফেলেছে-পানি না দিয়েও তাদের চাওয়া-পাওয়া পূরণ হচ্ছে। বাংলাদেশে নিজস্ব জাতীয় পানি নীতি না থাকায় আমরা নির্ভরশীল অন্য দেশের ওপর। যদিও চীনের সহায়তায় ৫০ বছরের ‘তিস্তা মহাপরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু চীন বা ভারত কেউই ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণ বন্ধ করবে না।
গজলডোবা বাঁধের কারণে প্রায়শই তিস্তা নদীতে হঠাৎ করে পানি ছেড়ে দেওয়া হয়, যা প্রতি বছর তীরবর্তী মানুষের জীবন ও জীবিকা বিপর্যস্ত করে। তাই শুধু বাঁধ নির্মাণ নয়, ভারতের সঙ্গে তিস্তা চুক্তিও অত্যন্ত জরুরি। নদীর এই সংকট আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জোরালোভাবে তুলে ধরতে হবে।
অবজার্ভার রিসার্চ ফাউন্ডেশনের তথ্যমতে, ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের ৪০ শতাংশ মানুষ বিশুদ্ধ পানি থেকে বঞ্চিত হবে। এই পরিসংখ্যানই বোঝায় কেন চীন তিব্বতের পানি নিয়ে আধিপত্য বিস্তার করতে চায়, কেন ভারতও একইভাবে তিব্বতকে কৌশলগতভাবে কাছে টানছে। কারণ দক্ষিণ এশিয়ার বিশুদ্ধ পানির প্রধান উৎস হিমালয় ও তিব্বত অঞ্চল।
তিস্তার দাবি আজ যদি আদায় হয়, তাহলে কাল সিলেটের বরাক নদীর টিপাইমুখ বাঁধ নিয়েও প্রশ্ন উঠবে, ফেনীর ডুম্বুর বাঁধ নিয়েও আলোচনার দাবি উঠবে। কিন্তু ভারত চায় না বাংলাদেশে এমন দাবি উঠুক-আর বাংলাদেশেও নদী নিয়ে গণআন্দোলন খুব কমই হয়।
২০২৪ সালের ফেনীর বন্যায় সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর তথ্যমতে প্রায় ১ বিলিয়ন ডলারের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এই ক্ষতি কি শুধু টাকায় পরিমাপ করা সম্ভব? মানুষের সারাজীবনের কষ্ট, জীবিকার ধ্বংস-এসব কি কেবল ত্রাণ দিয়ে পূরণ করা যায়?
তাই প্রয়োজন জাতীয় পর্যায়ের পানি নীতি এবং নদীভিত্তিক সুপরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মসূচি, যাতে জনগণের অংশগ্রহণ থাকে। আজকের এই মশাল মিছিল সেই সচেতনতার সূচনা-যা একদিন আলোকিত করবে বাংলার ১২৯৪টি নদী ও ৫৭টি আন্তর্জাতিক নদীর ন্যায্য পানির অধিকার।
লেখক : রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট, বাংলাদেশ সেন্টার ফর ইন্ডো-প্যাসিফিক অ্যাফেয়ার্স
- এমআই